জন্মদিনে মৃত্যুর কথা বলা কি ঠিক? জন্মদিনের মানেই তো নতুনের আবাহন। চির নতুনের ডাকে নতুন করে ভাবতে শেখা। সেই নতুনের মাঝে মৃত্যুর কথা কেন?
কারণ আর কিছুই নয়, মৃত্যু যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন গানের কাছে ফিরতে চাইছেন সুকুমার রায়। কবিতার কাছে ফিরতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ। একটা পরম আনন্দ যেন থেকে যায় গান আর কবিতার ভেতর। এবং চলে যাওয়ার পথটাকে কোনোভাবেই তা অমসৃণ করে তোলে না।
সে কথাই বলব আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে।
সুকুমার রায়কে খুব ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। যখন বেঁচে ছিলেন সুকুমার, তখন বিভিন্ন মানুষের কাছে সুকুমারের প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। কিন্তু কোনো চিঠিতে কিংবা কোনো লেখায় তার প্রমাণ নেই। সুকুমারের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালে, মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে। আজ থেকে ঠিক এক শ বছর আগে। ১৯৪০ সালে সুকুমার রায়ের ‘পাগলা দাশু’ প্রকাশের সময় সুকুমার-পত্নী সুপ্রভা রায়ের অনুরোধে বইটির ভূমিকাস্বরূপ সুকুমারকে নিয়ে এই কথাগুলো লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ:
‘সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে, তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেইজন্যই তিনি তার বৈপরীত্ব্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যাঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়াছে, কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যচ্ছাস্যের বিশেষত্ব তার প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না।’
১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেত যান, তখন ছাপাখানা নিয়ে আরও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে সেখানে ছিলেন সুকুমার রায়। সে যাত্রায় কবির সঙ্গে অনেক অন্তরঙ্গতা হয়েছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন তিনি। ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে যে লেকচার দিয়েছিলেন তিনি, সেখানে অন্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে ১৯২১ সালের ২১ জুন সুকুমার রায় একটি চিঠি লিখেছিলেন বোন পুণ্যলতাকে। সে চিঠির কয়েকটি লাইন এ রকম, ‘পরশুদিন মি. পিয়ারসন তাঁর বাড়িতে আমার বেঙ্গলি লিটারেচার সম্বন্ধে একটি পেপার পড়বার নেমন্তন্ন করেছিলেন…সেখানে গিয়ে দেখি মি. অ্যান্ড মিসেস আরনল্ড, মি. অ্যান্ড মিসেস রটেনস্টাইন, ড. পিসি রায়, মিসেস সর্বাধিকারী প্রভৃতি অনেক পরিচিত। তাছাড়া কয়েকজন অচেনা সাহেব মেম উপস্থিত। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে আছেন। বুঝতেই পারছিস আমার কী অবস্থা। যা হোক, চোখ কান বুঁজে পড়ে ছিলাম। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে বইটই এনে ম্যাটেরিয়াল জোগাড় করতে হয়েছিল। তা ছাড়া রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা—(সুদূর, পরশ পাথর, সন্ধ্যা, কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ ইত্যাদি ট্রান্সলেট করেছিলাম। মি. ক্রানমার বিং (নর্থব্রুক সোসাইটির সেক্রেটারি, ‘আর উইজডম অব দি ইস্ট’ সিরিজের এডিটর) খুব খুশি।…আমাকে ধরেছেন আরো ট্রান্সলেট করতে, তিনি পাবলিশ করবেন।’
১৯১৩ সালের ২১ জুলাই লন্ডনের ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট সোসাইটিতে সুকুমার রায় ‘দ্য স্পিরিট অব রবীন্দ্রনাথ’ নামে যে প্রবন্ধটি পড়েন, সেটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভারতীয়দের পক্ষে প্রথম পাবলিক ভাষণ। সে সময় ছয় মাস আমেরিকায় কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরে লন্ডনের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।
সে বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ সিটি অব লাহোর জাহাজে করে লন্ডন থেকে ভারতের উদ্দেশে রওনা হন। ২০ দিন ধরে চলেছিল সে জাহাজ। সে ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের পাশে ছিলেন কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার রায়।
সুকুমার রায়ের বিয়ে হয় সে বছরেই। বিলেত থেকে ফেরার পর। যখন বিয়ে হয়, তখন কলকাতায় ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। জমিদারির কাজে শিলাইদহে ছিলেন। বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছেলের বিয়েতে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সুকুমার রায় নিজেও কবিকে বিয়েতে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন।
কলকাতার বাইরে থাকার অজুহাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। কিন্তু বিয়ের লগ্নের আগেই বাড়ির বাইরে শোরগোল উঠল কেন, তা দেখতে এসে অভ্যাগতদের মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। শত বাধা পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই হাজির হয়েছেন সুকুমার রায়ের বিয়েতে। সুকুমার রায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহের টান ছিল এতটাই প্রবল।
স্বল্প আয়ু নিয়ে জন্মেছিলেন সুকুমার রায়। কিন্তু এই স্বল্প সময়টির প্রতিটি মুহূর্তই বুঝি সৃষ্টিশীল কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষ করে শিশু ও কিশোর সাহিত্যকে তিনি যে কোথায় নিয়ে গেলেন, সে তো তাঁর ‘হ য ব র ল’ কিংবা ‘পাগলা দাশু’ পড়লেই টের পাওয়া যায়। আর জীবজন্তু নিয়ে তাঁর যে লেখাগুলো, তার তুলনা আজ অবধি কি আছে?
সুকুমার রায় দুরারোগ্য কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে সুকুমার যখন শেষ শয্যা নিলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ছত্রিশ বছর। যখন তিনি বুঝলেন, বাঁচার আর আশা নেই, তখন শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন—রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাই।
রবীন্দ্রনাথ এলেন সুকুমার রায়ের কাছে। রবীন্দ্রনাথকে দেখে সুকুমার রায় অনুরোধ করলেন, ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু’ গানটি করতে। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন সে গান।
এরপর সুকুমার আরও একটি গান শুনতে চাইলেন। ‘দুঃখ এ নয়, সুখ নয়গো, গভীর শান্তি এ যে’ ছিল পরের গান। রবীন্দ্রনাথ এই গানটি শোনালেন দুবার। সুকুমার রায়ের হৃদয় ভরে উঠল। এর কিছুদিন পরেই জীবনের পথচলা শেষ হলো সুকুমার রায়ের।
মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রসংগীত
নিজের মৃত্যু বিষয়ে কুমার জয়ন্তনাথ রায়কে ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘শান্তিপূর্ণ মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করিনি। ভয় করি অপঘাত মৃত্যুকে। যদি মৃত্যুর পূর্বে হাসিমুখে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি, তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করি না।’
প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যায় পাওয়া যাবে এই কথাগুলো।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সে রকম মৃত্যু আসেনি। অস্ত্রোপচারের পর মারা গেলেন তিনি। মৃত্যুর আগে পেলেন খুব যন্ত্রণা। রবীন্দ্রনাথ অস্ত্রোপচারের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা ভেবেছিলেন, তাঁর এই অসুখ থেকে মুক্তি পেতে হলে অস্ত্রোপচারই একমাত্র পথ।
১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে যখন তিনি কালিম্পঙে গেলেন, তখন সেখানেই তাঁর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছিল ইউরিনের গন্ডগোল আর প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের সমস্যাই তাঁকে ২২শে শ্রাবণ বা ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে অকস্মাৎ জীবনের যবনিকা ঘটিয়েছিল।
গোটা জীবনই সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে পার করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম যে বড় অসুখ হয়েছিল তাঁর, সেটার নাম ছিল ইরিসিপেলাস।
রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হলেও চাইতেন না কেউ তাঁর ঘরে থাকুক। নিজ দেহে কারও হাতের স্পর্শ পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছিলেন একবার, ‘দৈহিক সেবা নিতান্ত অবান্তর। আসল জিনিস হচ্ছে স্নিগ্ধ সঙ্গ। যতক্ষণ পাই, ততক্ষণ লাভ।’
১৯৪১ সালের ১৩ মে। কিছুদিন আগেই পালিত হয়েছে ২৫শে বৈশাখ। অসুস্থ শরীরেই এদিন এল কবিতার ডাক। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা, গায়ে জ্বর। তারই মধ্যে বলে উঠলেন, ‘রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।’
বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিলেন। একটু পর কথা খুঁজে পেয়ে বললেন, ‘রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ, চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়।’
বড় ক্লান্ত তিনি। এটুকু বলে ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে বললেন, ‘বাকিটা লেখ।’ রানী চন্দ লিখে নিলেন, ‘সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা…।’
লেখালেখি চলছে, কিন্তু শরীর ভেঙে পড়ছে। শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ২৫ জুলাই বা ৯ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথকে আসতে হলো শান্তিনিকেতন ছেড়ে। কলকাতার সেই বাড়িতে, যে বাড়িতে তিনি জন্মেছিলেন।
২৭ জুলাই ভোরেই কবিতা ভর করল তাঁকে। রানী চন্দকে বললেন, ‘লিখে রাখ।’
`প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে
কে তুমি?
মেলে নি উত্তর।’
একটু বলেন, একটু থামেন।
‘বৎসর বৎসর চলে গেল
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি?
পেল না উত্তর।’
এরপর রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত রানী চন্দ, রানী মহলানবীশ, অমিতা ঠাকুর, নন্দিনী কৃপালনীকে দেখলেন শয্যাপাশে। বললেন, ‘বিপদে মোরে রক্ষা করো’ কবিতাটি শুনতে চাই।
নিজেই বললেন, ‘দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।’
৩০ জুলাই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর শেষ কবিতা—
তোমার সৃষ্টির পথ
রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী—
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে…।’
কবিতায় কিছু গোলমাল আছে, পরে ঠিক করে নেবেন বলে জানালেন।
সেদিনই অপারেশন হলো রবীন্দ্রনাথের শরীরে। ডা. লোলিতমোহন ব্যানার্জি করলেন অপারেশন। কিন্তু অপারেশনের পর শরীর আর ভালো হয়নি। ৩ আগস্ট থেকে তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ৫ আগস্ট থেকে জ্ঞান ছিল না কবির।
এই মর্ত্যজীবনে রবীন্দ্রনাথের শেষ খাবার ছিল দেড় আউন্স আখের রস আর আধ আউন্স বার্লি। আখের রস খেয়েছিলেন সন্ধ্যা ছটায়, আর বার্লি খেয়েছিলেন রাত নটায়।
২২ শ্রাবণ দুপুর দুটোর দিকে রবীন্দ্রনাথের পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। হৃদস্পন্দন থেমে যেতে থাকল। ১২টা ১০ মিনিটে থেমে গেল সব।
পৃথিবী যেন বিড়বিড় করে উঠল,
‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে…’
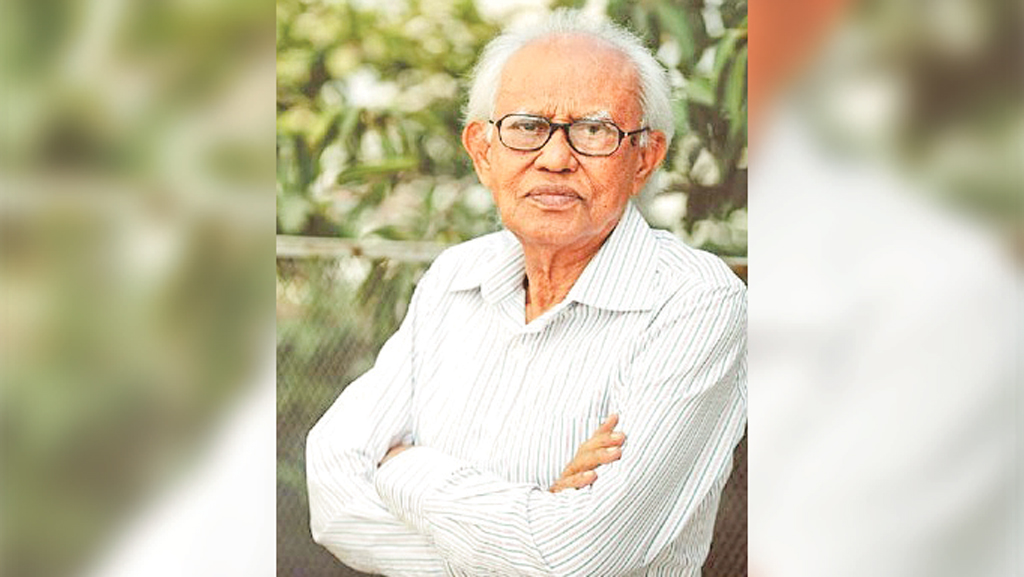
স্মৃতিচারণা করে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক বলেন, ‘যতদূর মনে পড়ে তখন দুটো-আড়াইটা হবে। ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ এবং পরিষদ ভবনসংলগ্ন এলাকা তখন ধোঁয়াচ্ছন্ন রণক্ষেত্র। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ১নং রুম কন্ট্রোল রুমে পরিণত হয়। মাওলানা তর্কবাগীশ, ধীরেন দত্ত, শামসুদ্দীন ও কংগ্রেস পার্টির সদস্যরা পরিষদ বয়কট...
৩ দিন আগে
সাঈদ হায়দার স্মৃতিচারণা করেছেন এভাবে: ‘দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, সংঘর্ষের তীব্রতা কমল না। প্রতিবাদমুখর ছাত্র-জনতাকে পুলিশ লাঠি চালিয়ে শান্ত করতে পারল না। তারা গুলি চালালো, গুলি চালালো মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের সামনের রাস্তায়। জব্বার আর রফিক প্রাণ হারালো।
৫ দিন আগে
মোহাম্মদ সুলতান ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী এবং একুশের প্রথম সংকলনের প্রকাশক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেকোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা রাত ১টায় ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী সিঁড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হই।
১০ দিন আগে
২১ ফেব্রুয়ারির আগে-পরের বছরগুলোজুড়ে নানা কিছু ঘটছিল। এখন এসে দিনগুলোতে ফিরে গেলে শিহরণ বোধ করি, বাংলা ভাষা নিয়ে এখন কিছু হতে দেখলে সেসব দিনে ফিরে যাই। তেমনই একটা হলো ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ সমাবর্তন সভা। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন—ঢাকাতেই, উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।
১১ দিন আগে