সম্পাদকীয়
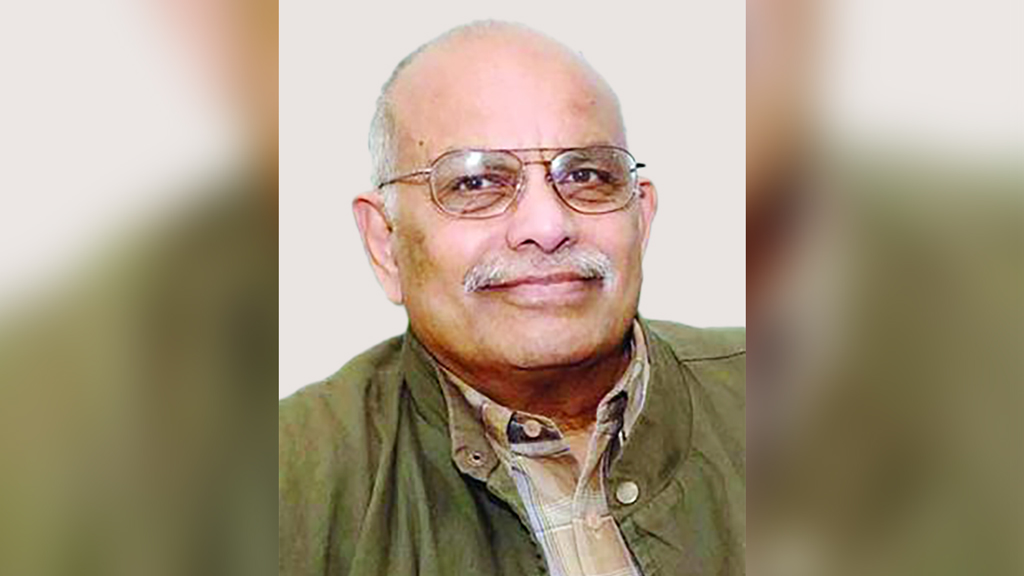
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয় ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...’ অমর পঙ্ক্তিমালা, যার রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে খ্যাতিমান এই মানুষটি গোটা জীবন কাটিয়েছেন লেখালেখি করেই। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। আমৃত্যু কলম ছাড়েননি।
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর গদ্যরীতি পাঠককে আকর্ষণ করত। রাজনৈতিক কলাম তাঁর কারণেই পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর মতো রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক পাওয়া কঠিন। জন্ম ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে। স্থানীয় মাদ্রাসায় এবং হাইস্কুলে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে আইএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করেন।
বাবার মৃত্যুর পর জীবিকার প্রয়োজনে বরিশালে গিয়ে ‘কংগ্রেস হিতৈষী’ পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। বরিশাল শহরে তিনি কিছুদিন মার্ক্সবাদী দল আরএসপির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে ‘সওগাত’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয়। এরপর ঢাকায় তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ‘দৈনিক ইনসাফ’ পত্রিকায় যোগ দিয়ে। এরপর একে একে কাজ করেছেন দৈনিক সংবাদ, মিল্লাত, ইত্তেফাক, আজাদ, পূর্বদেশসহ বিভিন্ন পত্রিকায়। ১৯৫৩ সালে মাসিক ‘সওগাত’ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন তিনি। তিনি মাসিক ‘নকীব’-এর সম্পাদক এবং ‘দিলরুবা’ পত্রিকারও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হন। তিনি সাহিত্য পত্রিকা ‘মেঘনা’ এবং রাজনৈতিক পত্রিকা ‘চাবুক’-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের নিবন্ধিত প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক ‘জয় বাংলা’র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।
‘দৈনিক জনপদ’-এর সম্পাদক থাকাকালীন ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান। এর পর থেকেই তাঁর প্রবাসজীবনের শুরু।
‘চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান’, ‘সম্রাটের ছবি’, ‘ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা’, ‘বাঙালি না বাংলাদেশী’ এবং নাটক ‘পলাশী থেকে বাংলাদেশ’, ‘একজন তাহমিনা’ ও ‘রক্তাক্ত আগস্ট’সহ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৩০টির মতো।
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ২০২২ সালের ১৯ মে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।
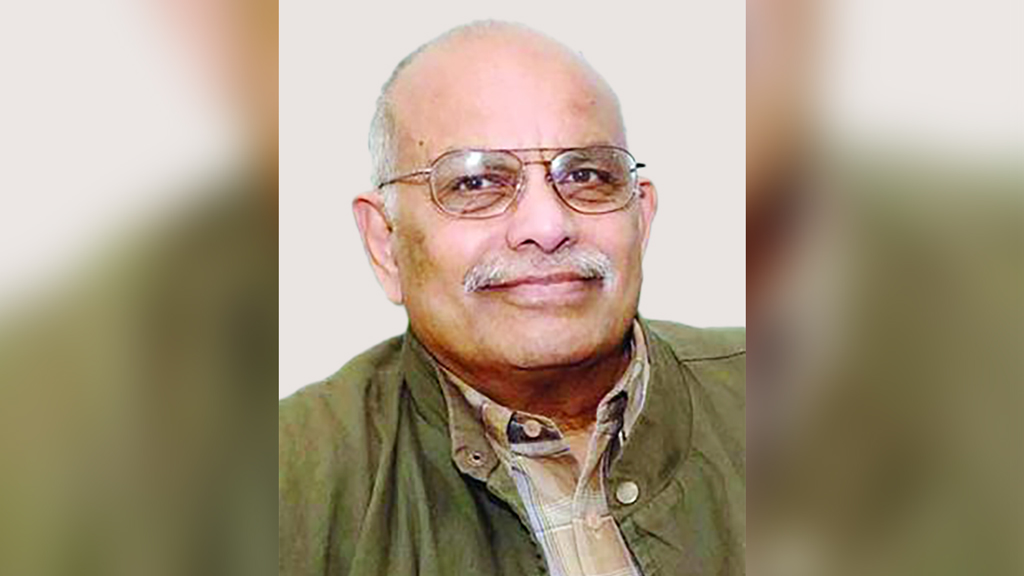
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয় ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...’ অমর পঙ্ক্তিমালা, যার রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে খ্যাতিমান এই মানুষটি গোটা জীবন কাটিয়েছেন লেখালেখি করেই। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। আমৃত্যু কলম ছাড়েননি।
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর গদ্যরীতি পাঠককে আকর্ষণ করত। রাজনৈতিক কলাম তাঁর কারণেই পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর মতো রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক পাওয়া কঠিন। জন্ম ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে। স্থানীয় মাদ্রাসায় এবং হাইস্কুলে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে আইএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করেন।
বাবার মৃত্যুর পর জীবিকার প্রয়োজনে বরিশালে গিয়ে ‘কংগ্রেস হিতৈষী’ পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। বরিশাল শহরে তিনি কিছুদিন মার্ক্সবাদী দল আরএসপির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে ‘সওগাত’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয়। এরপর ঢাকায় তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ‘দৈনিক ইনসাফ’ পত্রিকায় যোগ দিয়ে। এরপর একে একে কাজ করেছেন দৈনিক সংবাদ, মিল্লাত, ইত্তেফাক, আজাদ, পূর্বদেশসহ বিভিন্ন পত্রিকায়। ১৯৫৩ সালে মাসিক ‘সওগাত’ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন তিনি। তিনি মাসিক ‘নকীব’-এর সম্পাদক এবং ‘দিলরুবা’ পত্রিকারও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হন। তিনি সাহিত্য পত্রিকা ‘মেঘনা’ এবং রাজনৈতিক পত্রিকা ‘চাবুক’-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের নিবন্ধিত প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক ‘জয় বাংলা’র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।
‘দৈনিক জনপদ’-এর সম্পাদক থাকাকালীন ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান। এর পর থেকেই তাঁর প্রবাসজীবনের শুরু।
‘চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান’, ‘সম্রাটের ছবি’, ‘ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা’, ‘বাঙালি না বাংলাদেশী’ এবং নাটক ‘পলাশী থেকে বাংলাদেশ’, ‘একজন তাহমিনা’ ও ‘রক্তাক্ত আগস্ট’সহ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৩০টির মতো।
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ২০২২ সালের ১৯ মে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের ভানুগাছ সড়কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স-সংলগ্ন ভুরভুরিয়াছড়ার পাশেই বধ্যভূমি ৭১ পার্ক অবস্থিত। সেখানে প্রাচীন একটি বটগাছ রয়েছে, যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করে। পাকিস্তান আমলে গাছটির নিচে ছিল এক সাধুর আস্তানা।
৭ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর রেলস্টেশনের কাছেই রয়েছে একটি বধ্যভূমি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে সহযোগীদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী রহনপুর ও আশপাশের এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং অনেক সাধারণ বাঙালিকে এই বধ্যভূমিতে বিভিন্ন সময় ধরে এনে হত্যা করে।
৪ দিন আগে
আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ঘনিষ্ঠ হওয়ার। হাসান আজিজুল হকের সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। পরে তাঁর সঙ্গে প্রচুর আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন তুমুল আড্ডাবাজ মানুষ। আর তাঁর সঙ্গে জগৎ সংসারের যেকোনো বিষয়ে আলাপ করা যেত। এমন কোনো বিষয় নেই যাতে তাঁর আগ্রহ নেই।
৫ দিন আগে
১৯৭১ সালে পুরো বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু রাজধানীর মিরপুর তখনো শত্রুদের দখলে। পরের বছর জানুয়ারিতে শত্রুমুক্ত হলে একে একে সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে বধ্যভূমিগুলোর। ঢাকায় সবচেয়ে বেশি বধ্যভূমি মিরপুর অঞ্চলে। আর মিরপুরের বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাশ পাওয়া যায়...
৬ দিন আগেসম্পাদকীয়

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের ভানুগাছ সড়কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স-সংলগ্ন ভুরভুরিয়াছড়ার পাশেই বধ্যভূমি ৭১ পার্ক অবস্থিত। সেখানে প্রাচীন একটি বটগাছ রয়েছে, যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করে। পাকিস্তান আমলে গাছটির নিচে ছিল এক সাধুর আস্তানা। চা-শ্রমিক ও বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে এসে পূজা দিত, মনোবাসনা পূরণে মানত করত। সবাই জায়গাটিকে চিনত ‘সাধু বাবার থলি’ নামে। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এখানে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। হত্যার আগে বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে তাঁদের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বজন ও মুক্তিকামী সাধারণ মানুষও বাদ যাননি। গাছের ডালে উল্টো করে বেঁধে রাখা হতো তাঁদের। নির্যাতনের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তাঁরা শহীদ হন। সেই সব শহীদের ত্যাগকে অমর করে রাখতে এখানে নির্মিত হয় ‘বধ্যভূমি ৭১’ নামের স্মৃতিস্তম্ভটি। একাত্তরের স্মৃতিবিজড়িত বধ্যভূমিটিতে আরও রয়েছে ‘মৃত্যুঞ্জয়ী ৭১’ নামে একটি ভাস্কর্য।
ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের ভানুগাছ সড়কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স-সংলগ্ন ভুরভুরিয়াছড়ার পাশেই বধ্যভূমি ৭১ পার্ক অবস্থিত। সেখানে প্রাচীন একটি বটগাছ রয়েছে, যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করে। পাকিস্তান আমলে গাছটির নিচে ছিল এক সাধুর আস্তানা। চা-শ্রমিক ও বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে এসে পূজা দিত, মনোবাসনা পূরণে মানত করত। সবাই জায়গাটিকে চিনত ‘সাধু বাবার থলি’ নামে। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এখানে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। হত্যার আগে বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে তাঁদের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বজন ও মুক্তিকামী সাধারণ মানুষও বাদ যাননি। গাছের ডালে উল্টো করে বেঁধে রাখা হতো তাঁদের। নির্যাতনের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তাঁরা শহীদ হন। সেই সব শহীদের ত্যাগকে অমর করে রাখতে এখানে নির্মিত হয় ‘বধ্যভূমি ৭১’ নামের স্মৃতিস্তম্ভটি। একাত্তরের স্মৃতিবিজড়িত বধ্যভূমিটিতে আরও রয়েছে ‘মৃত্যুঞ্জয়ী ৭১’ নামে একটি ভাস্কর্য।
ছবি: সংগৃহীত
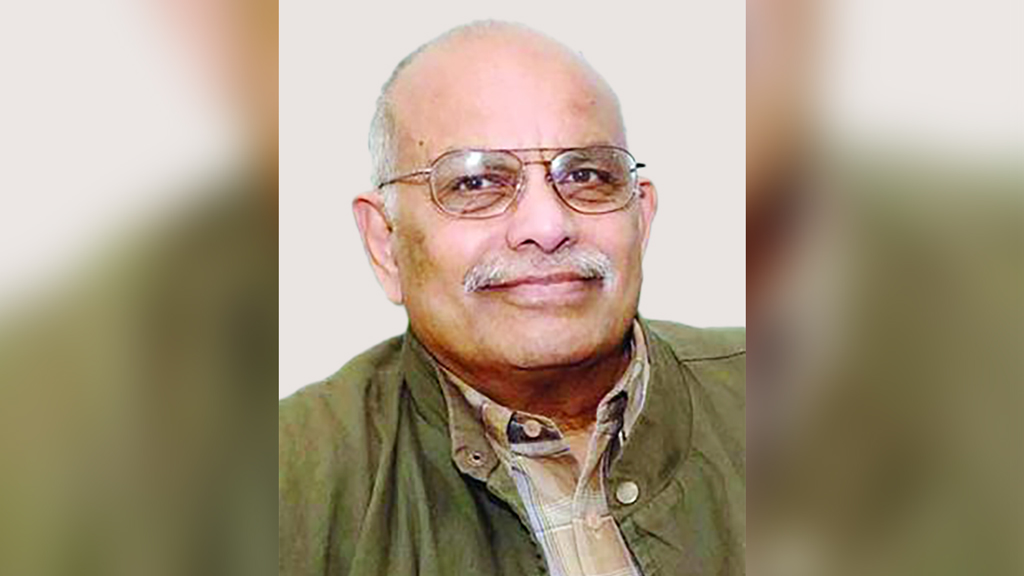
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয় ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...’ অমর পঙ্ক্তিমালা, যার রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে খ্যাতিমান এই মানুষটি গোটা জীবন কাটিয়েছেন লেখালেখি করেই। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। আমৃত্যু কলম ছাড়েননি।
১২ ডিসেম্বর ২০২৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর রেলস্টেশনের কাছেই রয়েছে একটি বধ্যভূমি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে সহযোগীদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী রহনপুর ও আশপাশের এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং অনেক সাধারণ বাঙালিকে এই বধ্যভূমিতে বিভিন্ন সময় ধরে এনে হত্যা করে।
৪ দিন আগে
আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ঘনিষ্ঠ হওয়ার। হাসান আজিজুল হকের সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। পরে তাঁর সঙ্গে প্রচুর আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন তুমুল আড্ডাবাজ মানুষ। আর তাঁর সঙ্গে জগৎ সংসারের যেকোনো বিষয়ে আলাপ করা যেত। এমন কোনো বিষয় নেই যাতে তাঁর আগ্রহ নেই।
৫ দিন আগে
১৯৭১ সালে পুরো বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু রাজধানীর মিরপুর তখনো শত্রুদের দখলে। পরের বছর জানুয়ারিতে শত্রুমুক্ত হলে একে একে সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে বধ্যভূমিগুলোর। ঢাকায় সবচেয়ে বেশি বধ্যভূমি মিরপুর অঞ্চলে। আর মিরপুরের বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাশ পাওয়া যায়...
৬ দিন আগেসম্পাদকীয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর রেলস্টেশনের কাছেই রয়েছে একটি বধ্যভূমি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে সহযোগীদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী রহনপুর ও আশপাশের এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং অনেক সাধারণ বাঙালিকে এই বধ্যভূমিতে বিভিন্ন সময় ধরে এনে হত্যা করে। শহীদদের সংখ্যাটা প্রায় ১০ হাজার! রহনপুর সরকারি এ বি উচ্চবিদ্যালয়ে ছিল পাকিস্তানিদের ক্যাম্প। এখানেও শত শত মানুষকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। বধ্যভূমির যে স্থানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সেখানেই শহীদদের সম্মানে নির্মিত হয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এই বধ্যভূমিটি রহনপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবর নামে পরিচিত।
ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর রেলস্টেশনের কাছেই রয়েছে একটি বধ্যভূমি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে সহযোগীদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী রহনপুর ও আশপাশের এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং অনেক সাধারণ বাঙালিকে এই বধ্যভূমিতে বিভিন্ন সময় ধরে এনে হত্যা করে। শহীদদের সংখ্যাটা প্রায় ১০ হাজার! রহনপুর সরকারি এ বি উচ্চবিদ্যালয়ে ছিল পাকিস্তানিদের ক্যাম্প। এখানেও শত শত মানুষকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। বধ্যভূমির যে স্থানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সেখানেই শহীদদের সম্মানে নির্মিত হয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এই বধ্যভূমিটি রহনপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবর নামে পরিচিত।
ছবি: সংগৃহীত
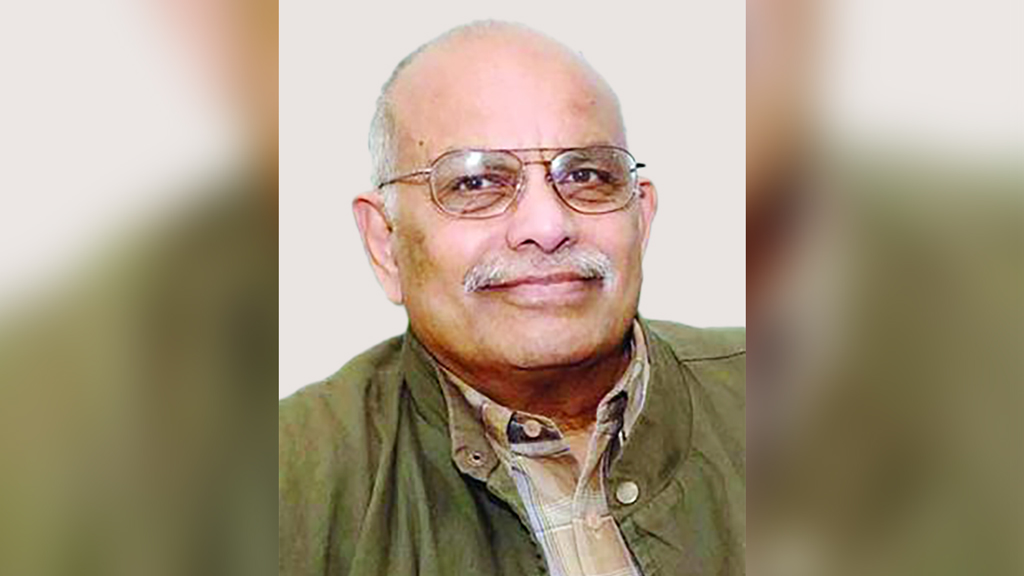
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয় ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...’ অমর পঙ্ক্তিমালা, যার রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে খ্যাতিমান এই মানুষটি গোটা জীবন কাটিয়েছেন লেখালেখি করেই। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। আমৃত্যু কলম ছাড়েননি।
১২ ডিসেম্বর ২০২৪
মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের ভানুগাছ সড়কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স-সংলগ্ন ভুরভুরিয়াছড়ার পাশেই বধ্যভূমি ৭১ পার্ক অবস্থিত। সেখানে প্রাচীন একটি বটগাছ রয়েছে, যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করে। পাকিস্তান আমলে গাছটির নিচে ছিল এক সাধুর আস্তানা।
৭ মিনিট আগে
আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ঘনিষ্ঠ হওয়ার। হাসান আজিজুল হকের সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। পরে তাঁর সঙ্গে প্রচুর আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন তুমুল আড্ডাবাজ মানুষ। আর তাঁর সঙ্গে জগৎ সংসারের যেকোনো বিষয়ে আলাপ করা যেত। এমন কোনো বিষয় নেই যাতে তাঁর আগ্রহ নেই।
৫ দিন আগে
১৯৭১ সালে পুরো বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু রাজধানীর মিরপুর তখনো শত্রুদের দখলে। পরের বছর জানুয়ারিতে শত্রুমুক্ত হলে একে একে সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে বধ্যভূমিগুলোর। ঢাকায় সবচেয়ে বেশি বধ্যভূমি মিরপুর অঞ্চলে। আর মিরপুরের বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাশ পাওয়া যায়...
৬ দিন আগেসম্পাদকীয়

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ঘনিষ্ঠ হওয়ার। হাসান আজিজুল হকের সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। পরে তাঁর সঙ্গে প্রচুর আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন তুমুল আড্ডাবাজ মানুষ। আর তাঁর সঙ্গে জগৎ সংসারের যেকোনো বিষয়ে আলাপ করা যেত। এমন কোনো বিষয় নেই যাতে তাঁর আগ্রহ নেই। তাঁর সাক্ষাৎকারে এমন কিছু প্রসঙ্গে আলাপ করেছি, যা হয়তো অত স্বচ্ছন্দে হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে করতে পারতাম না। যেমন ধরেন যৌনতা-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো। তবে আড্ডাবাজ ব্যক্তিত্বের জন্যও তাঁর সাক্ষাৎকারটি হয়েছে অনেক প্রাণবন্ত। তাঁকে তো বাম ঘরানার লেখকই ধরা হয়, মার্ক্সবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তবে তিনি কিন্তু গোঁড়া মার্ক্সবাদী ছিলেন না।
আমি এ ব্যাপারটিও তাঁর সঙ্গে খোলাসা করার জন্য আলাপ করেছি। সোশ্যালিস্ট রিয়েলিজমের নামে একসময় একধরনের যান্ত্রিক মার্ক্সবাদ চর্চা হয়েছে সাহিত্যে। তিনি এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এ সাক্ষাৎকারেই বলেছেন, এ দেশের মার্ক্সবাদীদের অনেক জ্ঞান থাকলেও কাণ্ডজ্ঞান নেই। তিনি তাঁর লেখায় জীবনকে একেবারে ভেতর থেকে ধরার চেষ্টা করেছেন। অহেতুক শ্রমিকশ্রেণির জয়গান গাননি, লাল পতাকা ওঠাননি। আমার সাক্ষাৎকারে সেক্সের সঙ্গে ক্লাস পজিশনের সম্পর্ক নিয়ে কথা আছে। তিনি এও বলছেন, তাঁর চিলেকোঠার সেপাইয়ের রিকশাশ্রমিক হাড্ডি খিজির যে চরিত্র, তাকে তিনি মহান করে দেখাননি, শুধু শ্রমিকশ্রেণির বিজয়গাথা তিনি দেখাননি।
বরং হাড্ডি খিজির যে একটি লুম্পেন চরিত্র, তার ভেতর যে নানা জোচ্চুরি আছে, সেটাকেও দেখিয়েছেন। এই যে মানুষকে টোটালিটিতে দেখতে এবং দেখাতে পারা, এটাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শক্তি।
তো এগুলো নিয়ে বিভিন্ন সময় কথা হতো তাঁর সঙ্গে, সেটাকেই আমি সাক্ষাৎকারে ধরতে চেষ্টা করেছি।
সূত্র: মঞ্জুরুল আজিম পলাশ কর্তৃক কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ‘দূরগামী কথার ভেতর’, পৃষ্ঠা: ২৭-২৮।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ঘনিষ্ঠ হওয়ার। হাসান আজিজুল হকের সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। পরে তাঁর সঙ্গে প্রচুর আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন তুমুল আড্ডাবাজ মানুষ। আর তাঁর সঙ্গে জগৎ সংসারের যেকোনো বিষয়ে আলাপ করা যেত। এমন কোনো বিষয় নেই যাতে তাঁর আগ্রহ নেই। তাঁর সাক্ষাৎকারে এমন কিছু প্রসঙ্গে আলাপ করেছি, যা হয়তো অত স্বচ্ছন্দে হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে করতে পারতাম না। যেমন ধরেন যৌনতা-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো। তবে আড্ডাবাজ ব্যক্তিত্বের জন্যও তাঁর সাক্ষাৎকারটি হয়েছে অনেক প্রাণবন্ত। তাঁকে তো বাম ঘরানার লেখকই ধরা হয়, মার্ক্সবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তবে তিনি কিন্তু গোঁড়া মার্ক্সবাদী ছিলেন না।
আমি এ ব্যাপারটিও তাঁর সঙ্গে খোলাসা করার জন্য আলাপ করেছি। সোশ্যালিস্ট রিয়েলিজমের নামে একসময় একধরনের যান্ত্রিক মার্ক্সবাদ চর্চা হয়েছে সাহিত্যে। তিনি এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এ সাক্ষাৎকারেই বলেছেন, এ দেশের মার্ক্সবাদীদের অনেক জ্ঞান থাকলেও কাণ্ডজ্ঞান নেই। তিনি তাঁর লেখায় জীবনকে একেবারে ভেতর থেকে ধরার চেষ্টা করেছেন। অহেতুক শ্রমিকশ্রেণির জয়গান গাননি, লাল পতাকা ওঠাননি। আমার সাক্ষাৎকারে সেক্সের সঙ্গে ক্লাস পজিশনের সম্পর্ক নিয়ে কথা আছে। তিনি এও বলছেন, তাঁর চিলেকোঠার সেপাইয়ের রিকশাশ্রমিক হাড্ডি খিজির যে চরিত্র, তাকে তিনি মহান করে দেখাননি, শুধু শ্রমিকশ্রেণির বিজয়গাথা তিনি দেখাননি।
বরং হাড্ডি খিজির যে একটি লুম্পেন চরিত্র, তার ভেতর যে নানা জোচ্চুরি আছে, সেটাকেও দেখিয়েছেন। এই যে মানুষকে টোটালিটিতে দেখতে এবং দেখাতে পারা, এটাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শক্তি।
তো এগুলো নিয়ে বিভিন্ন সময় কথা হতো তাঁর সঙ্গে, সেটাকেই আমি সাক্ষাৎকারে ধরতে চেষ্টা করেছি।
সূত্র: মঞ্জুরুল আজিম পলাশ কর্তৃক কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ‘দূরগামী কথার ভেতর’, পৃষ্ঠা: ২৭-২৮।
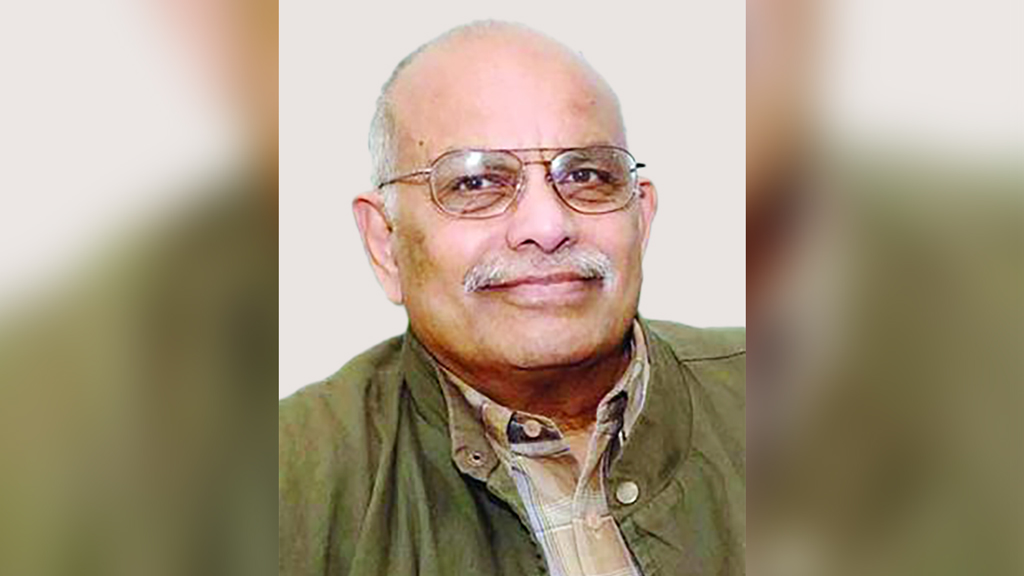
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয় ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...’ অমর পঙ্ক্তিমালা, যার রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে খ্যাতিমান এই মানুষটি গোটা জীবন কাটিয়েছেন লেখালেখি করেই। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। আমৃত্যু কলম ছাড়েননি।
১২ ডিসেম্বর ২০২৪
মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের ভানুগাছ সড়কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স-সংলগ্ন ভুরভুরিয়াছড়ার পাশেই বধ্যভূমি ৭১ পার্ক অবস্থিত। সেখানে প্রাচীন একটি বটগাছ রয়েছে, যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করে। পাকিস্তান আমলে গাছটির নিচে ছিল এক সাধুর আস্তানা।
৭ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর রেলস্টেশনের কাছেই রয়েছে একটি বধ্যভূমি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে সহযোগীদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী রহনপুর ও আশপাশের এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং অনেক সাধারণ বাঙালিকে এই বধ্যভূমিতে বিভিন্ন সময় ধরে এনে হত্যা করে।
৪ দিন আগে
১৯৭১ সালে পুরো বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু রাজধানীর মিরপুর তখনো শত্রুদের দখলে। পরের বছর জানুয়ারিতে শত্রুমুক্ত হলে একে একে সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে বধ্যভূমিগুলোর। ঢাকায় সবচেয়ে বেশি বধ্যভূমি মিরপুর অঞ্চলে। আর মিরপুরের বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাশ পাওয়া যায়...
৬ দিন আগেসম্পাদকীয়

১৯৭১ সালে পুরো বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু রাজধানীর মিরপুর তখনো শত্রুদের দখলে। পরের বছর জানুয়ারিতে শত্রুমুক্ত হলে একে একে সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে বধ্যভূমিগুলোর। ঢাকায় সবচেয়ে বেশি বধ্যভূমি মিরপুর অঞ্চলে। আর মিরপুরের বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাশ পাওয়া যায় শিয়ালবাড়ি এলাকায়। মিরপুরের প্রশিকা ভবন থেকে কমার্স কলেজের দিকে যেতে একটি কালভার্ট ছিল। এখন যদিও রাস্তার মাঝে ঢাকা পড়েছে। সেখানেই ৬০টি বস্তায় প্রায় ৩৫০টি মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল। সৈয়দ আলী জামে মসজিদের পাশের কুয়ায় পাওয়া গিয়েছিল অসংখ্য লাশ। ৬ নম্বর লেনের শেষ প্রান্তের মাঠে স্তূপাকারে পড়ে থাকা দুই শতাধিক লাশ শিয়ালবাড়ি গণকবরে কবর দেওয়া হয়। এটি ছিল ১০ কাঠা জমির ওপর। বেশির ভাগই দখল হয়ে গেছে। যেটুকু অংশ বাকি আছে, তা বর্তমানে মাতবরবাড়ি পারিবারিক কবরস্থান। শিয়ালবাড়ির যেসব কুয়ায় শহীদদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে এখন বহুতল ভবন, কারখানা, শপিং মল।
তথ্য ও ছবি: মিরপুরের ১০টি বধ্যভূমি, মিরাজ মিজু

১৯৭১ সালে পুরো বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু রাজধানীর মিরপুর তখনো শত্রুদের দখলে। পরের বছর জানুয়ারিতে শত্রুমুক্ত হলে একে একে সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে বধ্যভূমিগুলোর। ঢাকায় সবচেয়ে বেশি বধ্যভূমি মিরপুর অঞ্চলে। আর মিরপুরের বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাশ পাওয়া যায় শিয়ালবাড়ি এলাকায়। মিরপুরের প্রশিকা ভবন থেকে কমার্স কলেজের দিকে যেতে একটি কালভার্ট ছিল। এখন যদিও রাস্তার মাঝে ঢাকা পড়েছে। সেখানেই ৬০টি বস্তায় প্রায় ৩৫০টি মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল। সৈয়দ আলী জামে মসজিদের পাশের কুয়ায় পাওয়া গিয়েছিল অসংখ্য লাশ। ৬ নম্বর লেনের শেষ প্রান্তের মাঠে স্তূপাকারে পড়ে থাকা দুই শতাধিক লাশ শিয়ালবাড়ি গণকবরে কবর দেওয়া হয়। এটি ছিল ১০ কাঠা জমির ওপর। বেশির ভাগই দখল হয়ে গেছে। যেটুকু অংশ বাকি আছে, তা বর্তমানে মাতবরবাড়ি পারিবারিক কবরস্থান। শিয়ালবাড়ির যেসব কুয়ায় শহীদদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে এখন বহুতল ভবন, কারখানা, শপিং মল।
তথ্য ও ছবি: মিরপুরের ১০টি বধ্যভূমি, মিরাজ মিজু
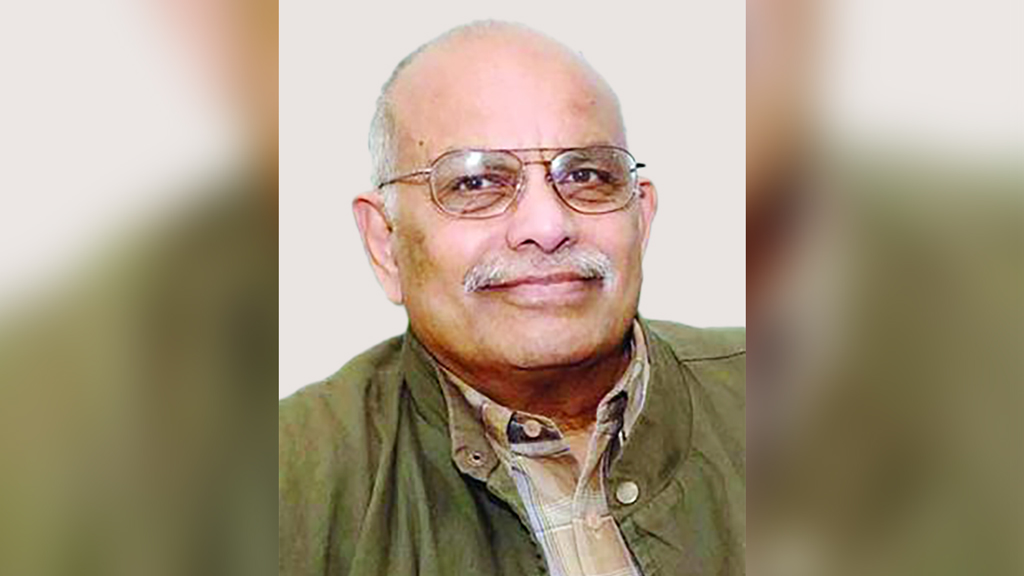
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয় ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...’ অমর পঙ্ক্তিমালা, যার রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে খ্যাতিমান এই মানুষটি গোটা জীবন কাটিয়েছেন লেখালেখি করেই। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। আমৃত্যু কলম ছাড়েননি।
১২ ডিসেম্বর ২০২৪
মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের ভানুগাছ সড়কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স-সংলগ্ন ভুরভুরিয়াছড়ার পাশেই বধ্যভূমি ৭১ পার্ক অবস্থিত। সেখানে প্রাচীন একটি বটগাছ রয়েছে, যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করে। পাকিস্তান আমলে গাছটির নিচে ছিল এক সাধুর আস্তানা।
৭ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর রেলস্টেশনের কাছেই রয়েছে একটি বধ্যভূমি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে সহযোগীদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী রহনপুর ও আশপাশের এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং অনেক সাধারণ বাঙালিকে এই বধ্যভূমিতে বিভিন্ন সময় ধরে এনে হত্যা করে।
৪ দিন আগে
আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ঘনিষ্ঠ হওয়ার। হাসান আজিজুল হকের সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। পরে তাঁর সঙ্গে প্রচুর আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন তুমুল আড্ডাবাজ মানুষ। আর তাঁর সঙ্গে জগৎ সংসারের যেকোনো বিষয়ে আলাপ করা যেত। এমন কোনো বিষয় নেই যাতে তাঁর আগ্রহ নেই।
৫ দিন আগে