বিভুরঞ্জন সরকার

দুর্নীতির দুই মামলার বিচার শেষে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দণ্ডিত করেছেন আদালত। এ নিয়ে বছরের পর বছর ধরে সরকার ও বিএনপির মধ্যে বাগ্যুদ্ধ চলছে। বিএনপি এই বিচারের রায় না মেনে বলে থাকে, ‘রাজনৈতিক কারণেই’ তিনি কারাগারে ছিলেন এবং কারাগারের বাইরে আছেন। বিএনপি খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করে সফল হয়নি। এখন খালেদা জিয়া রাজনীতি করতে পারবেন কি পারবেন না, তা নিয়ে সরকারের মন্ত্রীরা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়ে বিতর্ক তৈরি করছেন। মন্ত্রীদের এই বক্তব্যের পেছনেও যে রাজনীতি নেই, তা বলা যাবে না।
বিএনপি মনে করে, খালেদা জিয়া আইনের ঊর্ধ্বে; আইন ছুঁতে পারবে না তাঁকে। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হলেই বলার চেষ্টা করা হয়, এটা খালেদা জিয়ার ওপর আঘাত এবং এই আঘাতে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। যাঁরা এ ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই। কারণ গণতন্ত্র ও আইনের প্রতি আস্থাশীল যেকোনো ব্যক্তি, যদি তিনি রাজনীতিক হন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাঁর বলা উচিত—মামলা হয়েছে, আদালতে মোকাবিলা হবে। তিনি কখনোই ভাবতে পারেন না যে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হলেই গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানা হবে অথবা গণতন্ত্র তাতে দুর্বল হয়ে পড়বে। কোনো গণতন্ত্রকামী মানুষই ব্যক্তিকে, অর্থাৎ নিজেকে গণতন্ত্রের সমার্থক ভাবতে পারেন না। এ রকমটি ভাবেন স্বৈরাচারী শাসক, যিনি নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করেন। রাজনীতিতে ব্যক্তিকে আইনের ঊর্ধ্বে বা গণতন্ত্রের সমার্থক যিনি মনে করেন, তিনি মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও আসলে মানসিকতায় পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্রী।
আমাদের দেশে ক্ষমতায় থাকার সময় রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্ত হয় না, মামলা হওয়া তো দূরের কথা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে হয়তো এ রকম পরিস্থিতি থাকত না। গণতন্ত্রের প্রতি রাজনীতিবিদদের সত্যিকার অর্থে আস্থা থাকলেও এ রকমটি হতো না। নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে ভাবার মানসিকতা না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ক্ষমতাচ্যুতির পর মামলা করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভবই হতো না। তবে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলাগুলো প্রচলিত আইনের অধীনে, পূর্ণ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে এবং দেশে সংসদ ও সংবিধান কার্যকর থাকা অবস্থায় হওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা ভালো।
ক্ষমতাচ্যুতির পর, ক্ষমতা হারানোর পর বা পদত্যাগের পর অনেক সময় দেখা যায় ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে; তদন্ত হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচারও হয়েছে। আমাদের দেশেও হয়েছে। এর অনেকগুলোকেই প্রতিহিংসাপরায়ণতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ক্ষমতা হারানোর পর রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো আমাদের দেশে হয়েছে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে সামরিক সরকারের অধীনে পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে মামলা। যেমনটি জিয়াউর রহমানের আমলে আওয়ামী লীগের অনেক নেতার বিরুদ্ধে করা হয়েছিল; এরশাদের আমলে বিএনপির অনেক নেতার বিরুদ্ধেও হয়েছিল। সামরিক আদালতে তাঁদের কারও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের অনেককে কারাবরণ করতে হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, এই বিচারগুলো হয়েছে সামরিক শাসনামলে। সামরিক আইনের অধীনে এবং সামরিক আদালতে। এ-ও মনে রাখা প্রয়োজন, সামরিক আইন কোনো আইন নয়। এই বিচারগুলোতে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অর্থবহ ও আইনসম্মত কোনো সুযোগ ছিল না।
এবার একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বর্তমানে বিএনপি চেয়ারপারসন, বিরোধীদলীয় নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রের নামে দুটো বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন। জিয়াউর রহমানের মতো সামরিক শাসকদের তাদেরই সৃষ্ট সামরিক চক্রের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনাও কম নয় বিশ্বে। কিন্তু নিহত কারও বিধবা পত্নীকে রাষ্ট্রের নামে দু-দুটো বাড়ি দেওয়ার মতো ঘটনা বিশ্বে আর কোথাও আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। হতে পারে জিয়াউর রহমান ‘অসাধারণ’ সেনাপ্রধান ছিলেন। হতে পারে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নীও ‘অসাধারণ’ বলেই এই ধরনের রাষ্ট্রীয় উপহার। অথবা হতে পারে যাঁরা উপহার দিয়েছেন, তাঁদের অসাধারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এবং সেটা হাসিলের কৌশল হিসেবেই সহানুভূতির বাতাবরণে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রাষ্ট্রের নামে দু-দুটো বাড়ি দান করেছেন। বলা যায়, এ ছিল তাদের একধরনের ‘পলিটিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট’, যার ‘ডিভিডেন্ড’ পরে দাতারা পেয়েছেন। এই তথাকথিত রাষ্ট্রীয় দান কোনো অনিয়ম ছিল কি না, সেই প্রশ্ন ওঠা কি অস্বাভাবিক?
আমাদের দেশেই আরেকজন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর জীবিত নিকটাত্মীয়দের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাড়ি দেওয়া দূরের কথা, তাঁর ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটিতে বছরের পর বছর তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আইনের শাসনে বিশ্বাসী হলে এক দেশে দুই বিধান চলতে পারে না। ক্ষমতায় থেকে যা খুশি তাই করার স্বাধীনতার নাম কখনোই গণতন্ত্র নয়।
একটি বিষয়ে অবশ্যই ক্ষমতাসীনদের সতর্ক থাকতে হবে—কোনো মামলাই যেন কোনোভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপায় না হয়। কোনোভাবেই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মামলা করা না হয়। অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কিত অভিযোগে মামলা দায়ের করে আইনকে প্রভাবিত করে যেন কিছুতেই বিচারের নামে প্রহসন না করা হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ক্ষমতাসীন সরকারকেই। মামলাগুলো সম্পর্কে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও আইনকে নিজের গতিতে চলতে দেওয়ার বিষয়টি কঠোরভাবে পালনের প্রসঙ্গ আসে। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাফিলতি হলে সেটা হবে আইনকে প্রভাবিত করার সমতুল্য। এমন হলে মনে হবে যে, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মামলা হয়েছে।
মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের দেশে রাজনীতি বা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য যত আন্দোলন হয়েছে, ভাতের জন্য বা অর্থনৈতিক দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য তার এক শতাংশ আন্দোলনও হয়নি। তাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যত সমস্যা, তার চেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে রাজনীতিবিদদের মানসিকতায় এবং এটাই আসল সমস্যা। যত দিন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে অভিযোগের তদন্ত, মামলা বা বিচার সম্ভব হয়ে উঠছে না, তত দিন ক্ষমতাচ্যুতির পরই তা হতে থাকবে। এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে শাসক দলকে ক্ষমতায় থাকতেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অভিযোগ উত্থাপিত হলে সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রয়োজনে মামলা ও বিচার করার সুযোগও সৃষ্টি করতে হবে শাসক দলকেই। মুখে গণতন্ত্রের কথা বলব, ক্ষমতায় থাকার সময় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়াব; দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপিত হলে বলব রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হচ্ছে। নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে ভাবার এই মানসিকতা শুধু ক্ষমতাচ্যুতদের নয়, ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদদেরও পরিহার করতে হবে।
লেখক: জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা

দুর্নীতির দুই মামলার বিচার শেষে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দণ্ডিত করেছেন আদালত। এ নিয়ে বছরের পর বছর ধরে সরকার ও বিএনপির মধ্যে বাগ্যুদ্ধ চলছে। বিএনপি এই বিচারের রায় না মেনে বলে থাকে, ‘রাজনৈতিক কারণেই’ তিনি কারাগারে ছিলেন এবং কারাগারের বাইরে আছেন। বিএনপি খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করে সফল হয়নি। এখন খালেদা জিয়া রাজনীতি করতে পারবেন কি পারবেন না, তা নিয়ে সরকারের মন্ত্রীরা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়ে বিতর্ক তৈরি করছেন। মন্ত্রীদের এই বক্তব্যের পেছনেও যে রাজনীতি নেই, তা বলা যাবে না।
বিএনপি মনে করে, খালেদা জিয়া আইনের ঊর্ধ্বে; আইন ছুঁতে পারবে না তাঁকে। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হলেই বলার চেষ্টা করা হয়, এটা খালেদা জিয়ার ওপর আঘাত এবং এই আঘাতে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। যাঁরা এ ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই। কারণ গণতন্ত্র ও আইনের প্রতি আস্থাশীল যেকোনো ব্যক্তি, যদি তিনি রাজনীতিক হন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাঁর বলা উচিত—মামলা হয়েছে, আদালতে মোকাবিলা হবে। তিনি কখনোই ভাবতে পারেন না যে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হলেই গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানা হবে অথবা গণতন্ত্র তাতে দুর্বল হয়ে পড়বে। কোনো গণতন্ত্রকামী মানুষই ব্যক্তিকে, অর্থাৎ নিজেকে গণতন্ত্রের সমার্থক ভাবতে পারেন না। এ রকমটি ভাবেন স্বৈরাচারী শাসক, যিনি নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করেন। রাজনীতিতে ব্যক্তিকে আইনের ঊর্ধ্বে বা গণতন্ত্রের সমার্থক যিনি মনে করেন, তিনি মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও আসলে মানসিকতায় পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্রী।
আমাদের দেশে ক্ষমতায় থাকার সময় রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্ত হয় না, মামলা হওয়া তো দূরের কথা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে হয়তো এ রকম পরিস্থিতি থাকত না। গণতন্ত্রের প্রতি রাজনীতিবিদদের সত্যিকার অর্থে আস্থা থাকলেও এ রকমটি হতো না। নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে ভাবার মানসিকতা না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ক্ষমতাচ্যুতির পর মামলা করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভবই হতো না। তবে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলাগুলো প্রচলিত আইনের অধীনে, পূর্ণ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে এবং দেশে সংসদ ও সংবিধান কার্যকর থাকা অবস্থায় হওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা ভালো।
ক্ষমতাচ্যুতির পর, ক্ষমতা হারানোর পর বা পদত্যাগের পর অনেক সময় দেখা যায় ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে; তদন্ত হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচারও হয়েছে। আমাদের দেশেও হয়েছে। এর অনেকগুলোকেই প্রতিহিংসাপরায়ণতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ক্ষমতা হারানোর পর রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো আমাদের দেশে হয়েছে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে সামরিক সরকারের অধীনে পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে মামলা। যেমনটি জিয়াউর রহমানের আমলে আওয়ামী লীগের অনেক নেতার বিরুদ্ধে করা হয়েছিল; এরশাদের আমলে বিএনপির অনেক নেতার বিরুদ্ধেও হয়েছিল। সামরিক আদালতে তাঁদের কারও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের অনেককে কারাবরণ করতে হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, এই বিচারগুলো হয়েছে সামরিক শাসনামলে। সামরিক আইনের অধীনে এবং সামরিক আদালতে। এ-ও মনে রাখা প্রয়োজন, সামরিক আইন কোনো আইন নয়। এই বিচারগুলোতে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অর্থবহ ও আইনসম্মত কোনো সুযোগ ছিল না।
এবার একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বর্তমানে বিএনপি চেয়ারপারসন, বিরোধীদলীয় নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রের নামে দুটো বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন। জিয়াউর রহমানের মতো সামরিক শাসকদের তাদেরই সৃষ্ট সামরিক চক্রের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনাও কম নয় বিশ্বে। কিন্তু নিহত কারও বিধবা পত্নীকে রাষ্ট্রের নামে দু-দুটো বাড়ি দেওয়ার মতো ঘটনা বিশ্বে আর কোথাও আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। হতে পারে জিয়াউর রহমান ‘অসাধারণ’ সেনাপ্রধান ছিলেন। হতে পারে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নীও ‘অসাধারণ’ বলেই এই ধরনের রাষ্ট্রীয় উপহার। অথবা হতে পারে যাঁরা উপহার দিয়েছেন, তাঁদের অসাধারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এবং সেটা হাসিলের কৌশল হিসেবেই সহানুভূতির বাতাবরণে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রাষ্ট্রের নামে দু-দুটো বাড়ি দান করেছেন। বলা যায়, এ ছিল তাদের একধরনের ‘পলিটিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট’, যার ‘ডিভিডেন্ড’ পরে দাতারা পেয়েছেন। এই তথাকথিত রাষ্ট্রীয় দান কোনো অনিয়ম ছিল কি না, সেই প্রশ্ন ওঠা কি অস্বাভাবিক?
আমাদের দেশেই আরেকজন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর জীবিত নিকটাত্মীয়দের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাড়ি দেওয়া দূরের কথা, তাঁর ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটিতে বছরের পর বছর তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আইনের শাসনে বিশ্বাসী হলে এক দেশে দুই বিধান চলতে পারে না। ক্ষমতায় থেকে যা খুশি তাই করার স্বাধীনতার নাম কখনোই গণতন্ত্র নয়।
একটি বিষয়ে অবশ্যই ক্ষমতাসীনদের সতর্ক থাকতে হবে—কোনো মামলাই যেন কোনোভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপায় না হয়। কোনোভাবেই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মামলা করা না হয়। অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কিত অভিযোগে মামলা দায়ের করে আইনকে প্রভাবিত করে যেন কিছুতেই বিচারের নামে প্রহসন না করা হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ক্ষমতাসীন সরকারকেই। মামলাগুলো সম্পর্কে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও আইনকে নিজের গতিতে চলতে দেওয়ার বিষয়টি কঠোরভাবে পালনের প্রসঙ্গ আসে। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাফিলতি হলে সেটা হবে আইনকে প্রভাবিত করার সমতুল্য। এমন হলে মনে হবে যে, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মামলা হয়েছে।
মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের দেশে রাজনীতি বা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য যত আন্দোলন হয়েছে, ভাতের জন্য বা অর্থনৈতিক দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য তার এক শতাংশ আন্দোলনও হয়নি। তাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যত সমস্যা, তার চেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে রাজনীতিবিদদের মানসিকতায় এবং এটাই আসল সমস্যা। যত দিন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে অভিযোগের তদন্ত, মামলা বা বিচার সম্ভব হয়ে উঠছে না, তত দিন ক্ষমতাচ্যুতির পরই তা হতে থাকবে। এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে শাসক দলকে ক্ষমতায় থাকতেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অভিযোগ উত্থাপিত হলে সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রয়োজনে মামলা ও বিচার করার সুযোগও সৃষ্টি করতে হবে শাসক দলকেই। মুখে গণতন্ত্রের কথা বলব, ক্ষমতায় থাকার সময় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়াব; দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপিত হলে বলব রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হচ্ছে। নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে ভাবার এই মানসিকতা শুধু ক্ষমতাচ্যুতদের নয়, ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদদেরও পরিহার করতে হবে।
লেখক: জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা
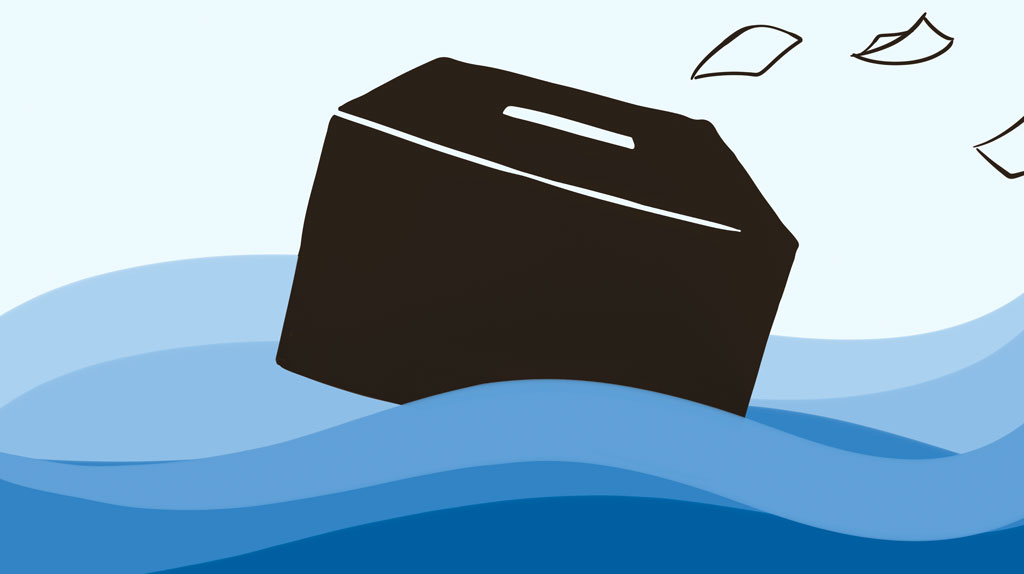
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটের পালে হাওয়া লাগা যাকে বোঝায়, সে রকম কোনো কিছু এখনো সাধারণ জনপরিসরে দেখা যাচ্ছে না। এবারই একসঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে একই দিনে। কিন্তু মানুষকে এখন পর্যন্ত নির্বাচনমুখী হতে দেখা যাচ্ছে না।
১৫ ঘণ্টা আগে
বর্তমান সময়ে চাকরি হলো সোনার হরিণ। যে হরিণের পেছনে ছুটছে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী। যেকোনো ধরনের চাকরি পেতে কারও প্রচেষ্টার যেন কোনো কমতি নেই। বিশেষ করে আমাদের দেশে সরকারি চাকরির বাজারে এখন প্রতিযোগিতার অভাব নেই।
১৫ ঘণ্টা আগে
সবকিছু ঠিক থাকলে ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্রপ্রত্যাশী জনগণের কাছে এই নির্বাচনটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। কারণ, এক যুগের বেশি সময় ধরে দেশে যে নির্বাচনী বাস্তবতা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ, অংশগ্রহণহীন এবং বিতর্কে ভরপুর।
১৫ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। দেশের নাগরিকেরা যেমন অধীর আগ্রহে দিনটির অপেক্ষা করছেন, তেমনি করছেন প্রবাসীরাও। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৩০০ সংসদীয় আসনে আগামী নির্বাচনের জন্য মোট ১৫ লাখ ২৭ হাজার ১৫৫ জন ভোটারের পোস্টাল ভোট নিবন্ধন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
১৫ ঘণ্টা আগে