
খবরটা প্রথমে টাচ করেনি। চলে গেলেন বেলা টার—এই বাক্যটা যেন একটু ধীরে চৈতন্যে এসে ঠেকল। তারপর মনে হলো, এই মানুষ তো সময়কে থোড়াই কেয়ার করেছেন, লেন্সের সামনে সময়কে দাঁড় করিয়ে সব তরিকায় অপদস্থ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর হজম হতে কিছুটা সময় নেওয়াই বরং স্বাভাবিক। আর তিনি তো ২০১১ সালেই চলে গিয়েছিলেন তুরিন হর্সের পর আর কোনো সিনেমা না বানানোর ঘোষণা দিয়ে। আজ তো শুধু আনুষ্ঠানিকতা।
বেলা টারের সিনেমা দেখতে বসলে মিস্টার টাইমকে বলে দিতাম, গেট আউট। সময় গুনলে তার সিনেমা দেখা যায় না। সেখানে মানুষ হাঁটে, বাতাস বয়, দরজা খোলে, কিন্তু আসলে কিছুই ঘটে না। আবার সবকিছুই ঘটে। এই ‘না-ঘটা’র মধ্যেই বেলা টারের জায়গা। দৃশ্যপট যখন দ্রুত হতে চায়, তখন তিনি ক্যামেরাকে থামিয়ে দেন। এই থামানোর মধ্যে এক বিদ্রোহী রাজনীতি রয়েছে বটে।
সেই রাজনীতি বুঝতে হলে আমাদের এক আত্মজিজ্ঞাসার আশ্রয় নিতে হবে। বেলা তারের মতো চলচ্চিত্রকারের জন্ম পূর্ব ইউরোপের দেশ হাঙ্গেরির মতো জায়গায় কেন হলো? যেখানে সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের বিকাশ, তার পতন ও মুক্তবাজারের আগ্রাসন—সিরিজটি চলছেই। বেলা টারের সিনেমা কি সেই দুর্বিষহ পরিক্রমার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ? হতে পারে, কেননা তাঁর সিনেমার নিরাশা কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়; সেটা ঐতিহাসিক। তাঁর দীর্ঘ শটগুলো যেন বলে—দেখো, সময় থামেনি, তাকে তাল দিতে গিয়ে মানুষ আশাহীন হয়ে গেছে।

শিল্পবিপ্লব ইউরোপকে গতি দিয়েছিল, কিন্তু সেই গতিই একসময় বোঝা হয়ে উঠল। মানুষ যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে নিজের ভেতরটা হারাতে শুরু করল। বেলা টারের সিনেমা কী সেই হারিয়ে যাওয়া সময়কে ফিরিয়ে আনার এক জেদি চেষ্টা। নিছক নস্টালজিয়া? সেই সমালোচনা হতেই পারে। তবে আজ সেই ক্ষণ নয়। আজ বেলা টার নেই। কিন্তু নৈঃশব্দটা থেকে গেল। সেটাই প্রাসঙ্গিক হোক।
ইউরোপীয় শিল্পচর্চার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, ওরা নিজেদের সভ্যতাকেই প্রশ্ন করে। ধর্ম, বিজ্ঞান, উন্নয়ন, প্রযুক্তি, প্রগতি—এই প্রত্যয়গুলোকে তারা ভক্তি করেছে, আবার প্রশ্নের বাণে বিদ্ধও করছে আজ অবধি। বেলা টার সেই ধারারই সন্তান। তিনি সিনেমায় ব্লকবাস্টারগিরি করেননি, প্লট টুইস্ট বা ক্লাইম্যাক্সও রাখেননি। তবে তিনি কি রেখে গেছেন? যার কারণে আমাদের কথা বলতে হয় তাঁর সিনেমা নিয়ে? তিনি শুধু যান্ত্রিক পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর গতির সঙ্গে লেন্সের তাল মেলাতে অস্বীকার করেছেন। এই নীরব অস্বীকৃতিই তাঁকে করে তুলেছে এক বিদ্রোহী। হয়ে উঠেছেন ইউরোপীয় সভ্যতার ক্লান্তির দর্পণ।
আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সিনেমায় কী বেলা টারের মতো কোনো চরিত্র রয়েছে? মাঝে মাঝে আমার এমন প্রশ্ন জাগত। তখন মনে হতো, জীবনানন্দ দাশ, বিনয় মজুমদার, উৎপল কুমার বসু—তাঁরা কী বেলা টারের এক ভিন্ন প্রতিচ্ছবি? এই বাংলার মাটি ও জলের ছোঁয়ায়? নাকি তা নয়, কেউ আসেনি অমন, শুধু আমরা নিজ সভ্যতাকে প্রশ্ন করতে পারঙ্গম নই বলে?
এই ত্রয়ী কবি তাঁদের সৃষ্টিকর্মে নৈঃশব্দ্যের কিছুটা পরশ আমাদের দিয়ে গেছেন বটে। জীবনানন্দ ধানসিঁড়ির ধারে এক নিশ্চল বিকেলকে রেখে গেছেন। বিনয় মজুমদার তো প্রেমকেও হিসাবের ভেতর ফেলে দেখতেন। দূরত্ব, পুনরাবৃত্তি, ক্লান্তি—সবকিছু এত নির্লিপ্তভাবে লিখতেন। শেষে গিয়ে কেবল মানুষের একাকিত্বটাই রয়ে যায়।
আর উৎপল কুমার বসুকে পড়লে একটা অস্বস্তি হয়। মনে হয়, আমাকে কেউ ইচ্ছা করে কবিতাটার ভেতর ঢুকতে দিচ্ছে না। বরং ঢুকবার ইচ্ছাকেই প্রবল করে তুলছে। বেলা টারের সিনেমাও ঠিক তেমনি অমোঘ। সে দর্শককে ডাকে না, অনুরোধ করে না। তুমি যদি থাকতে পারো, থাকো, না পারলে ফটক খোলা। তবে তাঁর সিনেম্যাটোগ্রাফিকে এড়ানো কি অতই সোজা?
আমার ধারণা, তাঁরা সবাই জানতেন, থামতে না পারলে শিল্প নষ্ট হয়। তাই তাঁরা থেমেছিলেন, স্বকীয়তায় ও স্ব-মহীমায়। বেলা টার ২০১১ সালের পর আর সিনেমা বানাননি। বলেছিলেন, ভাষার কাজ শেষ। এই কথা আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। কারণ, আমরা এমন সমাজে থাকি, যেখানে থামা মানেই হার।
বাংলাদেশের সিনেমা এখনো গল্পপ্রধান, তবু সেই গল্পের শরীরও আজকাল বেশ কৃশকায়। এখনো এখানকার সিংহভাগ দর্শককে নৈঃশব্দ্যের সৌন্দর্য দেখানোর চেষ্টা করলে হল ছেড়ে পালাবে। বেরিয়ে ভাঙচুর করবে বৈকি। বলবে, টাকাটা জলে গেল। অথচ আমাদের জীবনটাই তো অপেক্ষা আর নিঃশব্দে ভরা। যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি আর দীর্ঘশ্বাস—আমরা কবে স্ক্রিনে সেই রূঢ় জীবন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে শিখব? স্বাদ আস্বাদন করব বিষাদ ও শূন্যতার, অথবা ভাবব এর থেকে পরিত্রাণ নিয়ে।
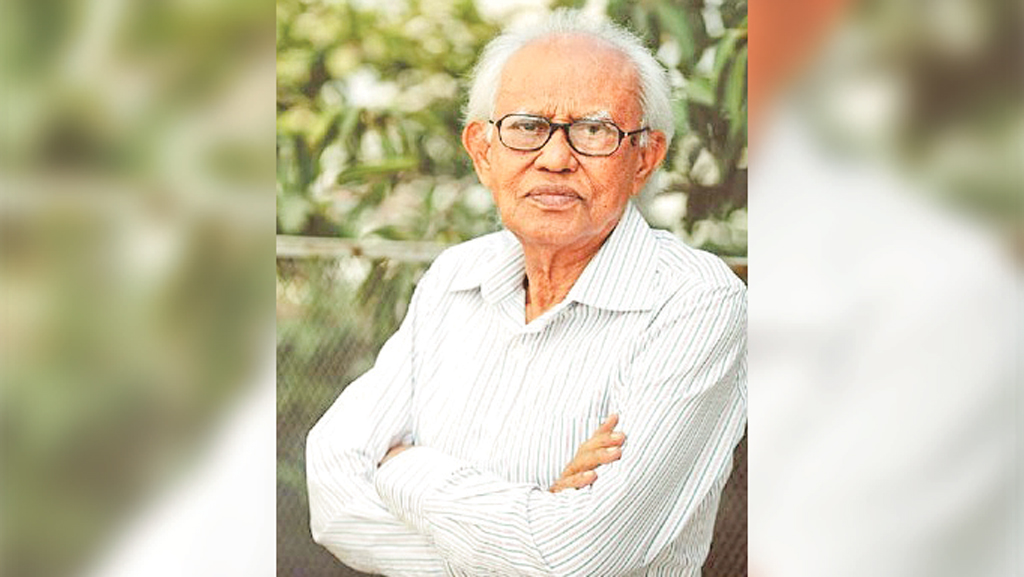
স্মৃতিচারণা করে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক বলেন, ‘যতদূর মনে পড়ে তখন দুটো-আড়াইটা হবে। ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ এবং পরিষদ ভবনসংলগ্ন এলাকা তখন ধোঁয়াচ্ছন্ন রণক্ষেত্র। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ১নং রুম কন্ট্রোল রুমে পরিণত হয়। মাওলানা তর্কবাগীশ, ধীরেন দত্ত, শামসুদ্দীন ও কংগ্রেস পার্টির সদস্যরা পরিষদ বয়কট...
২ দিন আগে
সাঈদ হায়দার স্মৃতিচারণা করেছেন এভাবে: ‘দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, সংঘর্ষের তীব্রতা কমল না। প্রতিবাদমুখর ছাত্র-জনতাকে পুলিশ লাঠি চালিয়ে শান্ত করতে পারল না। তারা গুলি চালালো, গুলি চালালো মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের সামনের রাস্তায়। জব্বার আর রফিক প্রাণ হারালো।
৪ দিন আগে
মোহাম্মদ সুলতান ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী এবং একুশের প্রথম সংকলনের প্রকাশক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেকোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা রাত ১টায় ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী সিঁড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হই।
৯ দিন আগে
২১ ফেব্রুয়ারির আগে-পরের বছরগুলোজুড়ে নানা কিছু ঘটছিল। এখন এসে দিনগুলোতে ফিরে গেলে শিহরণ বোধ করি, বাংলা ভাষা নিয়ে এখন কিছু হতে দেখলে সেসব দিনে ফিরে যাই। তেমনই একটা হলো ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ সমাবর্তন সভা। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন—ঢাকাতেই, উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।
১০ দিন আগে