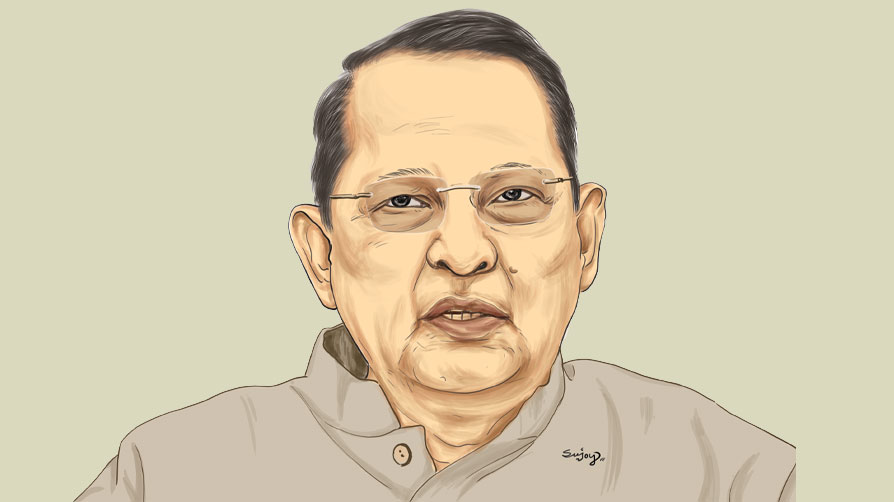
১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই দিনের মহানায়ক ছিলেন বীর উত্তম কর্নেল আবু তাহের। খলনায়ক ছিলেন বিশ্বাসঘাতক জেনারেল জিয়াউর রহমান। ৭ নভেম্বরের সিপাহি বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অনেক রকম আলোচনা-সমালোচনা হয়ে থাকে। আমি প্রথমেই বলতে চাই যে এটা সৈনিক হত্যা দিবসও না, মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবসও না, অফিসার হত্যা দিবসও না অথবা জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসও না। যাঁরা ওইভাবে বলার চেষ্টা করেন, তাঁরা কার্যত ইতিহাসকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। অবশ্য দেরিতে হলেও ধামাচাপা দেওয়া সত্য আজ প্রকাশিত হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে এখন সবাই সুস্পষ্টভাবে বলছেন, কারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, কারা জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছে, কারা বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকারী তথা মেজর ডালিম-ফারুক-রশীদ গংয়ের নিরাপদে দেশত্যাগ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তা সবই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এমনকি খালেদ মোশাররফকে কার নির্দেশে, কোন অফিসাররা হত্যা করেছে, খোদ খালেদ মোশাররফের পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের নামও প্রকাশ করা হয়েছে।
উল্লেখ থাকে যে, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দার—এই তিন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ৭ তারিখ সকাল বেলা দুজন ক্যাপ্টেন র্যাঙ্কের মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে। এ ব্যাপারে খালেদ মোশাররফের পরিবার নামধাম দিয়ে সব প্রকাশ করেছে। খালেদ মোশাররফের পক্ষে যেসব অফিসার ছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন লেখায় এ বিষয়গুলো প্রকাশ করেছেন।
১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা, ৩ নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যা, ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থান দমন, খালেদ মোশাররফ হত্যা, জিয়ার শাসনকালে কর্নেল তাহেরকে সাজানো মিথ্যা মামলায় বিচারের নামে প্রহসনে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা, সেনানিবাসে শত শত অফিসার হত্যার তদন্ত হওয়া দরকার। সব সত্য উদ্ঘাটন করা দরকার। সে জন্য আমি মনে করি, জাতীয় সত্য উদ্ঘাটন কমিশন গঠন করা বাংলাদেশের জন্য বাঞ্ছনীয়।
বঙ্গবন্ধু হত্যা ও চার জাতীয় নেতা হত্যার পর দেশে যে রাজনৈতিক সংকট ও শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তা দূর করতে ৭ নভেম্বর শহীদ কর্নেল আবু তাহের ও জাসদের নেতৃত্বে এবং সমর্থনে ঐতিহাসিক বিপ্লবী অভ্যুত্থানচেষ্টা ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের একটা সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু জেনারেল জিয়া ও তাঁর সহযোগী পাকিস্তানপন্থী অফিসার এবং দেশি-বিদেশি গোষ্ঠী সেই মহান বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে দমন করে দেশকে পাকিস্তানি ধারায় প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ঠেলে দেয়। জিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে শুরু করে।
৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থান কেন ঘটল এবং কী জন্য ঘটল? এ ব্যাপারে আমি বলব, ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা, ৩ নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা, অবৈধ ক্ষমতা দখল, সংবিধান লঙ্ঘন, সামরিক শাসন জারি, ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী অফিসারদের পাগলা কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি বন্ধ করতে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করতে এবং সেনাবাহিনীসহ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে ৭ তারিখের সিপাহি বিদ্রোহটা একটা মহান প্রচেষ্টা ছিল।
সিপাহি বিদ্রোহ তো হুট করে হয়নি। এর একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল। সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা কী? ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে অবৈধ ক্ষমতা দখল এবং সামরিক শাসন জারি করে উচ্ছৃঙ্খল খুনি চক্র ক্যান্টনমেন্টকে কার্যত বিভক্ত করেছিল। এর ধারাবাহিকতায় ৩ নভেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো অবৈধ ক্ষমতা দখলের ঘটনা ঘটে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে। সেদিন দিবাগত রাতে জেলহত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। তারপর খালেদ মোশাররফের সরাসরি ব্যবস্থাপনায় এবং জেনারেল ওসমানীর মধ্যস্থতায় বঙ্গবন্ধুর খুনিসহ ২৯ জনকে বাংলাদেশ ত্যাগ করে থাইল্যান্ডে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের শায়েস্তা করার জন্য নয়, নিজে ক্ষমতা দখলের জন্য খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান করেছিলেন। খুনি খন্দকার মোশতাককে আটক করা তো দূরের কথা, তাঁর সঙ্গেই যোগসাজশ করে নিজে সেনাপ্রধানের ব্যাজ লাগান।
সশস্ত্র বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নাম করে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে বন্দী করে সাংবিধানিক সরকার গঠনের দিকে না হেঁটে খালেদ মোশাররফ নিজেই ১৫ আগস্টের পরে আরেকবার চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করেন। খালেদ মোশাররফ বলপ্রয়োগ করে পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন এবং খন্দকার মোশতাককে দিয়ে সেনাপ্রধান হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন। খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধান হয়েও সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁর পুরো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন; বরং সশস্ত্র বাহিনীকে বিভক্ত করে আরও বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেন। খালেদ মোশাররফের ক্ষমতায়নের পর সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকেরা একে অপরের দিকে বন্দুক তাক করে গৃহযুদ্ধের অবস্থা তৈরি করেন। রক্তগঙ্গা বইয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা তৈরি হয়। খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করলেও দেশের সরকার গঠনে বিলম্ব করেন এবং ৩ থেকে ৬ নভেম্বর দেশে বাস্তবে কোনো সরকার ছিল না। রেডিও-টেলিভিশনের প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খালেদ মোশাররফ পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে বলপ্রয়োগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ১৫ আগস্টে খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী বিভক্ত হয় এবং খুনিরা নিয়ম ভঙ্গ করে বঙ্গভবনে তাদের অনুগত সৈনিকদের নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীকে সেনাপ্রধানের আওতার বাইরে খুনিদের আওতায় রাখা হয়। অথচ নতুন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেননি। ক্যান্টনমেন্ট সৈনিকদের নিরাপদ আস্তানার বদলে ক্ষমতালোভী অফিসারদের আস্তানায় পরিণত হয়। এ অবস্থায় খালেদ মোশাররফের ৩ নভেম্বর ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীতে কোর (Core) ও ইনফেন্ট্রি বা পদাতিক বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। ৩ নভেম্বর ফোর্থ বেঙ্গল দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন খালেদ মোশাররফ। ৬৪ জন অফিসারকে তিনি তড়িঘড়ি করে পদোন্নতি দেন। বঙ্গবন্ধুর সাংবিধানিক সরকারকে পুনর্বহাল করার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে খালেদ মোশাররফ নিজে ক্ষমতা দখল করার জন্য জেনারেল জিয়াকে বন্দী করেন এবং পার্লামেন্ট বাতিল করে দেন। তিনি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সায়েমকে নিয়ম ভঙ্গ করে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন। জেলখানায় জাতীয় চার নেতা, যাঁরা ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধেরও নেতা, যাঁদের খন্দকার মোশতাক বন্দী করেছিলেন, তাঁদের নিরাপত্তার দিকে তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। খালেদ মোশাররফের সহায়তায় খুনি চক্র দেশত্যাগ করলেও তাদের অনুগত আট শতাধিক সৈনিক বাংলাদেশে রেখে যায়। এরা সেনাবাহিনীর ভেতরে একটা দুষ্টচক্র হিসেবে থেকে যায়। তারাও একটা সমস্যা ক্যান্টনমেন্টে তৈরি করে বসে। অন্যদিকে খালেদ মোশাররফের ক্ষমতা দখলের পরে জেনারেল জিয়া কাপুরুষের মতো এটাকে মোকাবিলা না করে পদত্যাগপত্র দেন এবং পেনশনের টাকার জন্য দেনদরবার শুরু করেন খালেদের সঙ্গে। এসব ঘটনা পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে ফেলে। খালেদ মোশাররফ অবশেষে স্কেল এ অ্যালার্ট জারি করেন। এই অ্যালার্ট জারি করা মানে হচ্ছে, তিনি ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য বলপ্রয়োগ করবেন। ৫ নভেম্বর রংপুর থেকে টেন্থ বেঙ্গল ঢাকায় নিয়ে আসেন। মেজর নওয়াজিশ ও বাহাত্তর ব্রিগেড কর্নেল হুদার নেতৃত্বে ঢাকায় চলে আসে। এই সবকিছুই উত্তেজনা তৈরি করে।
 এ অবস্থায় জিয়ার অনুরোধে নারায়ণগঞ্জে অবস্থানরত সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া কর্নেল তাহের বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
এ অবস্থায় জিয়ার অনুরোধে নারায়ণগঞ্জে অবস্থানরত সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া কর্নেল তাহের বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
উল্লেখ্য, কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরে একটি বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কাজ চালু ছিল। এই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা অসহায় সৈনিকদের শৃঙ্খলার ভেতর রাখার জন্য এবং পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গোলাগুলি না করার জন্য শুরু থেকেই উদ্যোগ নিয়েছিল।
সিপাহি বিদ্রোহ হয় কেন?
১. গৃহযুদ্ধ থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে রক্ষার জন্য।
২. সশস্ত্র বাহিনীতে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতালোভী অফিসারদের কাছ থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে রক্ষার জন্য।
৩. বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনতে।
৪. বঙ্গবন্ধু হত্যার খুনি ও অবৈধ দখলদারদের কবল থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে উদ্ধার করার জন্য।
৫. সাংবিধানিক ধারায় বাংলাদেশকে আবার ফেরত আনার জন্য।
৬. রাজনীতিবিদদের দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সর্বদলীয় সরকার গঠনের জন্য।
৭. ঔপনিবেশিক চালচলন, রীতিনীতি, আইনকানুন পরিবর্তন করার জন্য।
ওপরের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে ও জাসদের সমর্থনে অবশেষে ৬ নভেম্বর গভীর রাতে অর্থাৎ ৭ নভেম্বর ভোরে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।
সিপাহি বিদ্রোহ কতটুকু সফল?
সিপাহি বিদ্রোহ গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে সফল হয়েছে। ক্যান্টনমেন্টে রক্তগঙ্গা বন্ধে সফল হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর খুনি ও সামরিক চক্রান্তকারীদের অপতৎপরতা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে এবং ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীতে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সফল হয়েছে এবং খন্দকার মোশতাকের পুনরায় ক্ষমতা দখল বানচাল করতে সফল হয়েছে।
৭ নভেম্বরের ব্যর্থতা কী?
সিপাহি বিদ্রোহ সাংবিধানিক শাসন ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। জিয়ার সমর্থক অফিসারদের চক্রান্ত বানচাল করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশ আবার জিয়ার সামরিক শাসনের বেড়াজালে আটকা পড়েছে। সিপাহি বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতির ওপর কর্নেল তাহের ও সৈনিক সংস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ৮ নভেম্বর থেকেই পুরো পরিস্থিতির ওপর জেনারেল জিয়া ও সামরিক অফিসাররা পূর্ণকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় সফল হন। কর্নেল তাহেরের সহায়তায় বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে জেনারেল জিয়া উল্টো তাঁর ত্রাতাদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। ২৩ নভেম্বর আমাকে, সদ্য মুক্ত আ স ম আবদুর রব, মেজর জলিলকে গ্রেপ্তার করে। ২৪ নভেম্বর কর্নেল তাহেরকে গ্রেপ্তার করে।
সিপাহিদের এই যে মহান প্রচেষ্টা, তা সম্পূর্ণ সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। কিন্তু ৭ নভেম্বর সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও দেশপ্রেমিক সিপাহিদের এক মহৎ উদ্যোগ ও বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ছিল।
কর্নেল তাহের ও জাসদ পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে না পারার জন্য জিয়ার চক্রান্ত সফল হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ৭ তারিখের সিপাহি বিদ্রোহের চেষ্টাটা ম্লান হয়ে যায়। আমি তুলনা করছি এভাবে, নব্বইয়ের স্বৈরাচারের পতনের পর খালেদা জিয়ার ক্ষমতায়ন শেখ হাসিনাসহ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির ক্ষমতা দখলের ব্যর্থতা গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের অন্যায্যতা প্রমাণ করে না বা নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান ম্লান হয়ে যায় না। ইতিহাসে অনেক ঘটনাই ঘটে। যে ঘটনা পরিপূর্ণতা পায় না। মোদ্দাকথা হলো, সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানচেষ্টা কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না, কোনো চক্রান্ত ছিল না, এককভাবে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাও ছিল না। এটি একটি দেশপ্রেমিক উদ্যোগই ছিল।
লেখক: এমপি, সাবেক মন্ত্রী, সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ভারতের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আদানি পাওয়ারের সঙ্গে অসম চুক্তির ব্যাপারটি নতুন ছিল না। সে সময়ও এটা নিয়ে প্রশ্ন ও সমালোচনা উঠেছিল। তারপরও সে সরকার দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে সে চুক্তি করেছিল। অন্তর্বর্তী সরকার আদানির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী বকেয়া টাকা পরিশোধ করেছিল।
৪ ঘণ্টা আগে
পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে গতকাল। এ সময় এলেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারকে একটি বড় পরীক্ষা দিতে হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সব সময় বলে আসছে, দেশে উৎপাদন ও আমদানি চাহিদার তুলনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বাস্তব ফল উল্টো। ফলমূল, সবজি, মুরগিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আগের মতো এবারেও বেড়েছে।
৪ ঘণ্টা আগে
আটচল্লিশে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শামিল হয়ে এদিন আত্মাহুতি দিয়েছিলেন বাংলার দামাল সন্তানেরা। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং একুশের চেতনার মশাল সমুন্নত রাখার এই সংগ্রাম বায়ান্নতেই...
৪ ঘণ্টা আগে
কেউ যে ঘুষ খায় না—এটাই যে বিস্ময়ের ব্যাপার হতে পারে, সেটা দেখা গেল রংপুরের এক ঘটনায়। কাগজে মোড়ানো এক গিফট বক্স নিয়ে যে ঘটনাটি ঘটে গেল, তা কাল্পনিক নাটকের ঘটনাকে ছাপিয়ে যায়। শিক্ষা কর্মকর্তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি গিফট বক্সের ভেতর ৭ লাখ টাকা নিয়ে আসেন।
১ দিন আগে