অবরুদ্ধ দেশের সাংবাদিকতা
জাহীদ রেজা নূর

সায়মন ড্রিং ও অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের প্রতিবেদনের কথা বলা হলো। আরও অনেক বিদেশি সাংবাদিকের নামও বলা যাবে, যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে এসে সরেজমিন দেখেছেন পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো নৃশংসতা। এখানে বলে রাখা দরকার, এই সাংবাদিকেরা কেবল তখনই তাঁদের প্রতিবেদন ছাপতে পেরেছেন, যখন পৌঁছে গেছেন নিরাপদ ঠিকানায়। পাকিস্তানে বসে এই লেখাগুলো প্রকাশ করা সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।
এখানে আরেকজন বিদেশি সাংবাদিকের কথাও বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সাংবাদিক তাঁদের দেশের পত্রিকায় প্রথম এই গণহত্যার কথা ছাপেন। আমরা ডান কগিনের কথা বলছি। তিনি ছিলেন টাইম ম্যাগাজিনের সংবাদদাতা। ২৫ মার্চের তাণ্ডবের পর যে সাংবাদিকদের ঢাকা থেকে বের করে দেয় পাকিস্তানি জান্তা, ডান কগিন ছিলেন তাঁদেরই একজন। ঢাকা থেকে বহিষ্কারের পর তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। সেখান থেকে মোটরসাইকেলে করে পুনরায় সীমান্ত অতিক্রম করেন। এরপর গোপনে বাসে-ট্রাকে-সাইকেলে করে ঢাকা শহরে ঢুকে পড়েন। ঢাকা থেকে খবর সংগ্রহ করে আবার ফিরে যান ভারতে। এরপর তিনি তাঁর ম্যাগাজিনের জন্য পাঠিয়ে দেন ইয়াহিয়ার কুকীর্তির খবর।
এপ্রিলে ঢাকা যে মৃত নগরী, সে কথা তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন কগিন। হাজার হাজার লোক এই
শহরে নিহত হয়েছেন এবং শহরের অর্ধেক মানুষ শহর থেকে পালিয়ে গেছেন। শহরের ১৮টি বাজারের ১৪টিই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ বইটিতে বাজার পুড়িয়ে দেওয়ার বর্ণনায় এ কথাও পেয়েছিলাম যে ঠাটারি বাজারে পশু কোরবানির পাশাপাশি কসাইদেরও জবাই করেছিল হানাদার বাহিনী।
সে সময় শহরের প্রায় সব বাড়িতেই উড়ত পাকিস্তানের পতাকা। জিন্নাহ এবং ইয়াহিয়ার ছবিও দেখা গেছে যত্রতত্র। কগিন বুঝে গেছেন, এগুলো বাহ্যিক বিষয়। বাঙালিদের মনে তখন জ্বলছে আগুন। যুদ্ধে তাদের হার হয়নি, এটা তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। প্রতিরোধ ও প্রতিরোধের স্পৃহা তখন বাঙালির মনে। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে বাঙালিরা তাঁর সামনে মেলে ধরেছে তাদের অভিজ্ঞতার ঝাঁপি। মসজিদ থেকে বৃদ্ধকে টেনেহিঁচড়ে বের করে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে বোঝানো হয়েছে বাঙালি মুসলমানরা আসলে ছদ্মবেশী হিন্দু।
পুরান ঢাকাকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। বাড়িগুলোয় পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ বাইরে পালাতে গেলে মেশিনগানের গুলি চালানো হয়েছে।
টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কগিনের প্রতিবেদনটি ছাপা হওয়ার পর ১১ মে তা কলকাতার ‘জয় বাংলা’ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। কগিন সে লেখায় মন্তব্য করেছিলেন, ‘বর্ষাকাল আসছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে ভয়ংকর সংকট। ইসলামাবাদকে হয়তো বুঝতে হবে, কেবল গায়ের জোরে একতা রক্ষা করা যায় না এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ ঠিক এমন পাকিস্তানের কথা কখনো চিন্তা করেননি।’
২৩ মে ভারতের ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় ‘সাংবাদিক নিহত’ শিরোনামে ছাপা একটি খবরে বলা হয়, ‘আর একটি বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, ইত্তেফাক পত্রিকার প্রাক্তন চিফ রিপোর্টার শ্রী খন্দকার আবু তালেব সম্প্রতি অবাঙালিদের হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন।’
খন্দকার আবু তালেব শহীদ হয়েছিলেন ২৯ মার্চ। একজন উর্দুভাষী অবাঙালি সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন তিনি। অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে প্রথম শহীদ সাংবাদিক হলেন খন্দকার আবু তালেব। শহীদ আবু তালেবের বাড়ি ছিল মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনে। মিরপুর এলাকা স্বাধীনতাবিরোধীদের আস্তানা ছিল। ২৪ মার্চ খন্দকার আবু তালেব তাঁর পরিবারের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চামেলীবাগে তাঁর বোনের বাড়িতে। ২৫ মার্চ তিনি সেখানে বন্ধু সিরাজুদ্দীন হোসেনের বাড়িতে যান। সেখান থেকে রাত ১০টার পর বাড়িতে ফেরার পর অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয়। চামেলীবাগের অবস্থান রাজারবাগের পাশেই। পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আসতে থাকেন আবু তালেবের বোনের বাড়িতে। ভয় পেয়ে তাঁরা দেয়াল টপকে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ২৭ মার্চ খন্দকার আবু তালেব সবাইকে নিয়ে বোনের বাড়িতে ফিরে আসেন। ২৮ তারিখে সান্ধ্য আইন শিথিল হলে তিনি ইত্তেফাক অফিসে যান। ২৫ মার্চ রাতেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ইত্তেফাক অফিস। তিনি ভস্মীভূত অফিসে কিছু লাশ দেখেন। মিরপুরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। মিরপুরে তখন মাথায় লালপট্টি বেঁধে বিহারিরা বাঙালিদের হত্যা করে বেড়াচ্ছিল। আবু তালেব মনস্থির করেছিলেন এই অবস্থায় তিনি মিরপুরে যাবেন না। কিন্তু নিয়তি তাঁকে মিরপুরেই টেনে নিয়ে যায়। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে ফুটে উঠত সেই অরাজকতা। কিন্তু ২৯ মার্চ তিনি মিরপুরে গেলে বিহারিরা তাঁকে জবাই করে। তাঁর লাশ খণ্ডবিখণ্ড
করে রাখা হয়।
রাজনীতিসচেতন ছিলেন খন্দকার আবু তালেব। আওয়ামী লীগের ছয় দফা বাংলায় অনুবাদ করে সান্ধ্য দৈনিক আওয়াজে ছেপেছিলেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের অনুবাদও করেছিলেন তিনি।
অবরুদ্ধ ঢাকায় মার্চের নৃশংসতার মধ্যেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা তখন রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।
জাহীদ রেজা নূর, উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

সায়মন ড্রিং ও অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের প্রতিবেদনের কথা বলা হলো। আরও অনেক বিদেশি সাংবাদিকের নামও বলা যাবে, যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে এসে সরেজমিন দেখেছেন পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো নৃশংসতা। এখানে বলে রাখা দরকার, এই সাংবাদিকেরা কেবল তখনই তাঁদের প্রতিবেদন ছাপতে পেরেছেন, যখন পৌঁছে গেছেন নিরাপদ ঠিকানায়। পাকিস্তানে বসে এই লেখাগুলো প্রকাশ করা সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।
এখানে আরেকজন বিদেশি সাংবাদিকের কথাও বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সাংবাদিক তাঁদের দেশের পত্রিকায় প্রথম এই গণহত্যার কথা ছাপেন। আমরা ডান কগিনের কথা বলছি। তিনি ছিলেন টাইম ম্যাগাজিনের সংবাদদাতা। ২৫ মার্চের তাণ্ডবের পর যে সাংবাদিকদের ঢাকা থেকে বের করে দেয় পাকিস্তানি জান্তা, ডান কগিন ছিলেন তাঁদেরই একজন। ঢাকা থেকে বহিষ্কারের পর তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। সেখান থেকে মোটরসাইকেলে করে পুনরায় সীমান্ত অতিক্রম করেন। এরপর গোপনে বাসে-ট্রাকে-সাইকেলে করে ঢাকা শহরে ঢুকে পড়েন। ঢাকা থেকে খবর সংগ্রহ করে আবার ফিরে যান ভারতে। এরপর তিনি তাঁর ম্যাগাজিনের জন্য পাঠিয়ে দেন ইয়াহিয়ার কুকীর্তির খবর।
এপ্রিলে ঢাকা যে মৃত নগরী, সে কথা তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন কগিন। হাজার হাজার লোক এই
শহরে নিহত হয়েছেন এবং শহরের অর্ধেক মানুষ শহর থেকে পালিয়ে গেছেন। শহরের ১৮টি বাজারের ১৪টিই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ বইটিতে বাজার পুড়িয়ে দেওয়ার বর্ণনায় এ কথাও পেয়েছিলাম যে ঠাটারি বাজারে পশু কোরবানির পাশাপাশি কসাইদেরও জবাই করেছিল হানাদার বাহিনী।
সে সময় শহরের প্রায় সব বাড়িতেই উড়ত পাকিস্তানের পতাকা। জিন্নাহ এবং ইয়াহিয়ার ছবিও দেখা গেছে যত্রতত্র। কগিন বুঝে গেছেন, এগুলো বাহ্যিক বিষয়। বাঙালিদের মনে তখন জ্বলছে আগুন। যুদ্ধে তাদের হার হয়নি, এটা তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। প্রতিরোধ ও প্রতিরোধের স্পৃহা তখন বাঙালির মনে। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে বাঙালিরা তাঁর সামনে মেলে ধরেছে তাদের অভিজ্ঞতার ঝাঁপি। মসজিদ থেকে বৃদ্ধকে টেনেহিঁচড়ে বের করে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে বোঝানো হয়েছে বাঙালি মুসলমানরা আসলে ছদ্মবেশী হিন্দু।
পুরান ঢাকাকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। বাড়িগুলোয় পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ বাইরে পালাতে গেলে মেশিনগানের গুলি চালানো হয়েছে।
টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কগিনের প্রতিবেদনটি ছাপা হওয়ার পর ১১ মে তা কলকাতার ‘জয় বাংলা’ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। কগিন সে লেখায় মন্তব্য করেছিলেন, ‘বর্ষাকাল আসছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে ভয়ংকর সংকট। ইসলামাবাদকে হয়তো বুঝতে হবে, কেবল গায়ের জোরে একতা রক্ষা করা যায় না এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ ঠিক এমন পাকিস্তানের কথা কখনো চিন্তা করেননি।’
২৩ মে ভারতের ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় ‘সাংবাদিক নিহত’ শিরোনামে ছাপা একটি খবরে বলা হয়, ‘আর একটি বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, ইত্তেফাক পত্রিকার প্রাক্তন চিফ রিপোর্টার শ্রী খন্দকার আবু তালেব সম্প্রতি অবাঙালিদের হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন।’
খন্দকার আবু তালেব শহীদ হয়েছিলেন ২৯ মার্চ। একজন উর্দুভাষী অবাঙালি সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন তিনি। অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে প্রথম শহীদ সাংবাদিক হলেন খন্দকার আবু তালেব। শহীদ আবু তালেবের বাড়ি ছিল মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনে। মিরপুর এলাকা স্বাধীনতাবিরোধীদের আস্তানা ছিল। ২৪ মার্চ খন্দকার আবু তালেব তাঁর পরিবারের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চামেলীবাগে তাঁর বোনের বাড়িতে। ২৫ মার্চ তিনি সেখানে বন্ধু সিরাজুদ্দীন হোসেনের বাড়িতে যান। সেখান থেকে রাত ১০টার পর বাড়িতে ফেরার পর অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয়। চামেলীবাগের অবস্থান রাজারবাগের পাশেই। পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আসতে থাকেন আবু তালেবের বোনের বাড়িতে। ভয় পেয়ে তাঁরা দেয়াল টপকে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ২৭ মার্চ খন্দকার আবু তালেব সবাইকে নিয়ে বোনের বাড়িতে ফিরে আসেন। ২৮ তারিখে সান্ধ্য আইন শিথিল হলে তিনি ইত্তেফাক অফিসে যান। ২৫ মার্চ রাতেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ইত্তেফাক অফিস। তিনি ভস্মীভূত অফিসে কিছু লাশ দেখেন। মিরপুরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। মিরপুরে তখন মাথায় লালপট্টি বেঁধে বিহারিরা বাঙালিদের হত্যা করে বেড়াচ্ছিল। আবু তালেব মনস্থির করেছিলেন এই অবস্থায় তিনি মিরপুরে যাবেন না। কিন্তু নিয়তি তাঁকে মিরপুরেই টেনে নিয়ে যায়। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে ফুটে উঠত সেই অরাজকতা। কিন্তু ২৯ মার্চ তিনি মিরপুরে গেলে বিহারিরা তাঁকে জবাই করে। তাঁর লাশ খণ্ডবিখণ্ড
করে রাখা হয়।
রাজনীতিসচেতন ছিলেন খন্দকার আবু তালেব। আওয়ামী লীগের ছয় দফা বাংলায় অনুবাদ করে সান্ধ্য দৈনিক আওয়াজে ছেপেছিলেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের অনুবাদও করেছিলেন তিনি।
অবরুদ্ধ ঢাকায় মার্চের নৃশংসতার মধ্যেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা তখন রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।
জাহীদ রেজা নূর, উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা
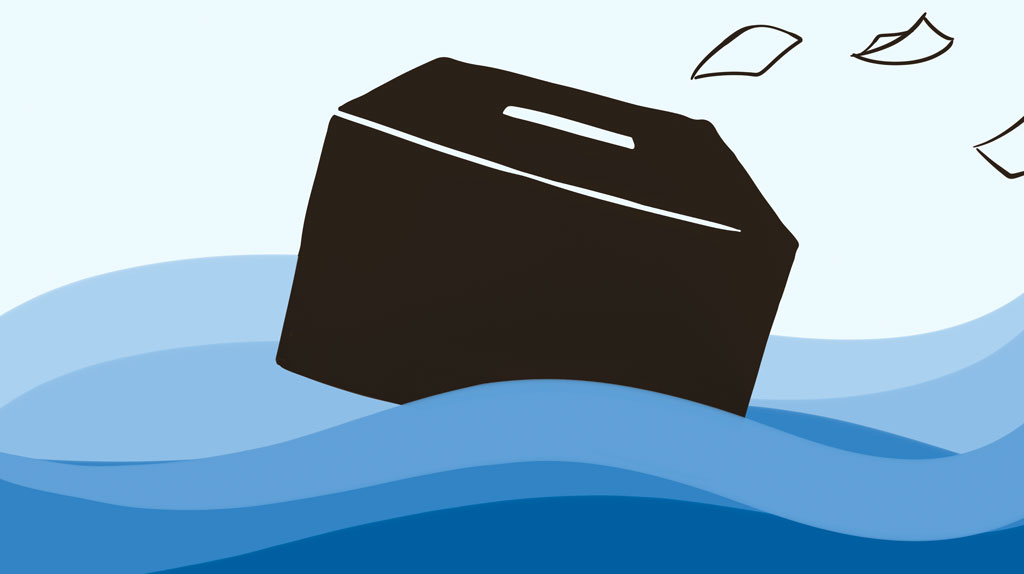
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটের পালে হাওয়া লাগা যাকে বোঝায়, সে রকম কোনো কিছু এখনো সাধারণ জনপরিসরে দেখা যাচ্ছে না। এবারই একসঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে একই দিনে। কিন্তু মানুষকে এখন পর্যন্ত নির্বাচনমুখী হতে দেখা যাচ্ছে না।
১ দিন আগে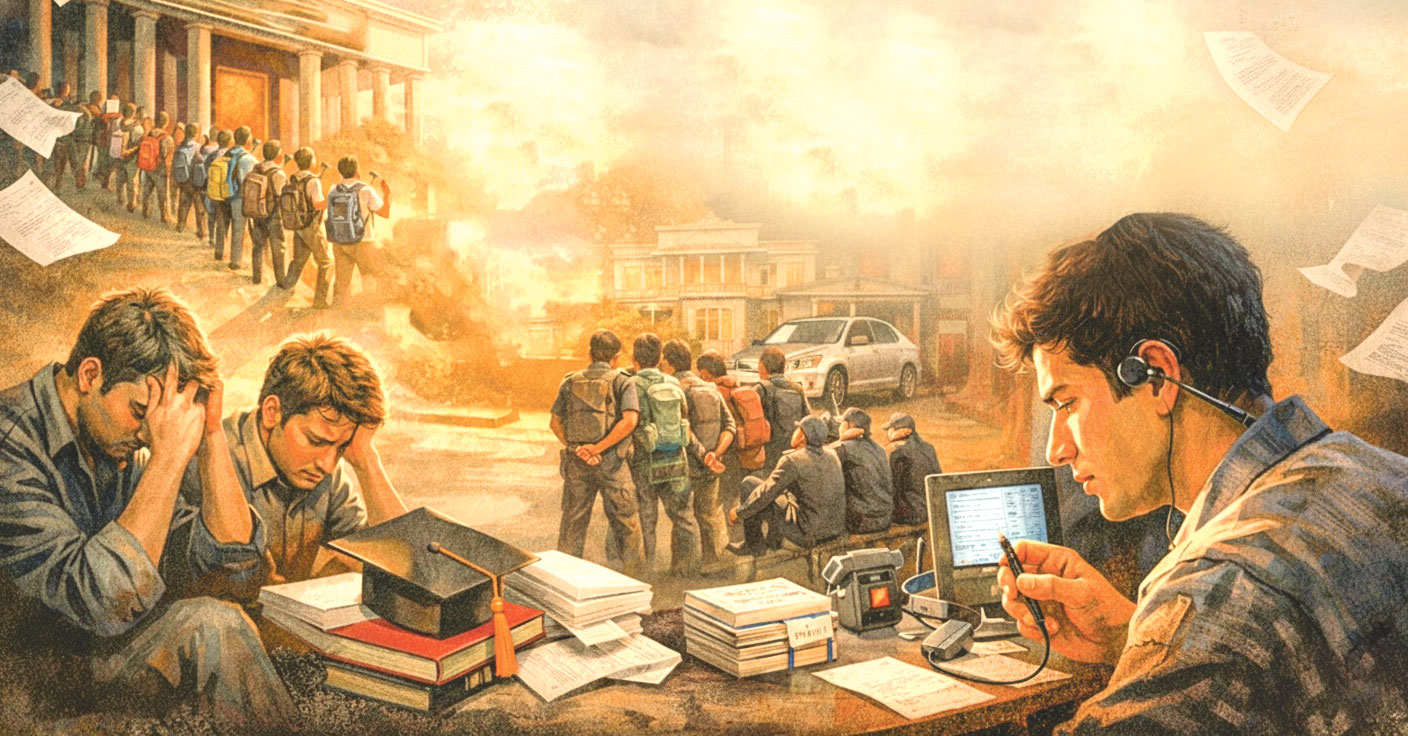
বর্তমান সময়ে চাকরি হলো সোনার হরিণ। যে হরিণের পেছনে ছুটছে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী। যেকোনো ধরনের চাকরি পেতে কারও প্রচেষ্টার যেন কোনো কমতি নেই। বিশেষ করে আমাদের দেশে সরকারি চাকরির বাজারে এখন প্রতিযোগিতার অভাব নেই।
১ দিন আগে
সবকিছু ঠিক থাকলে ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্রপ্রত্যাশী জনগণের কাছে এই নির্বাচনটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। কারণ, এক যুগের বেশি সময় ধরে দেশে যে নির্বাচনী বাস্তবতা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ, অংশগ্রহণহীন এবং বিতর্কে ভরপুর।
১ দিন আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। দেশের নাগরিকেরা যেমন অধীর আগ্রহে দিনটির অপেক্ষা করছেন, তেমনি করছেন প্রবাসীরাও। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৩০০ সংসদীয় আসনে আগামী নির্বাচনের জন্য মোট ১৫ লাখ ২৭ হাজার ১৫৫ জন ভোটারের পোস্টাল ভোট নিবন্ধন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
১ দিন আগে