
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ। তিনি মূলত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং এনজিও নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা হলো ‘বাংলাদেশে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং এনজিও’, যা ‘জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ’-এ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি জুলাই আন্দোলন, অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম, আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির বিতর্কসহ নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।
মাসুদ রানা

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের এক বছরের মূল্যায়নটা শুনতে চাই।
আমরা দেখেছি জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে শিক্ষার্থী-জনতা, এদের সঙ্গে অনেক রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন পেশার মানুষজন এবং শ্রমজীবী জনগণ যুক্ত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল বৈষম্যের বিরোধিতা। যদিও বৈষম্যের বিরোধিতাটা শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু এর মূল স্পিরিটটা এ দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে। বিগত সময়ের যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা জারি ছিল, সেটাও বৈষম্য সৃষ্টিকারী ছিল। তবে গণ-অভ্যুত্থানের পরে এ দেশের সবার প্রত্যাশা ছিল, আমাদের বাংলাদেশে বৈষম্যহীন সমাজের একটা ছবি সবার কাছে আস্তে আস্তে ভাসতে শুরু করবে। কিন্তু আমরা ক্রমান্বয়ে দেখতে পেলাম অভ্যুত্থানের পরপরই যে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চালু হলো, আমরা সেটার মধ্যে একটা বৈষম্যের রূপ দেখতে পেলাম। বিগত সময়ের সরকার যেভাবে দলীয়করণ করেছিল, আমরা দেখতে পেলাম অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হওয়ার পর একইভাবে দলীয়করণ করা শুরু করল। মানে যারা সরকারের স্টেকহোল্ডার, তাদের রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হলো। সেটা বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি যাদের কথাই বলেন না কেন। আমাদের যে নতুন বাংলাদেশের চিত্র দেখার প্রত্যাশা ছিল, সেটা শুরুতেই বিনষ্ট করা হয়েছে। শুধু বিনষ্ট না, বাধাগ্রস্তও করা হয়েছে। সরকার গঠনের পর শুরুতেই তাদের যে কাজটা করা দরকার ছিল বলে আমি মনে করি, সেটা হলো দেশের মধ্যে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য এক নম্বর গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেশের মানুষকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এখনো করছে। যেটা মব ভায়োলেন্সের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। মব ভায়োলেন্স প্রথম দিকে খুব তীব্র মাত্রায় ছিল। আবার এখন দেখা যাচ্ছে সেটা সারা দেশে আবারও বেড়ে গেছে। সুতরাং আমরা এই সরকারের কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম, সরকার তার অতি সামান্যই সফল করতে পেরেছে। যদিও তারা পাচার করা টাকা উদ্ধারের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের মধ্যে রেমিট্যান্স আসার প্রবাহটা বেড়েছে। কিন্তু অর্থনীতির সম্ভাবনার জায়গাগুলো দুর্বল অবস্থায় পড়ে আছে। বিশেষ করে বিনিয়োগ আসাটা একদম নেই বললে চলে।
অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ হওয়ার কারণ কী বলে মনে করেন?
সাধারণ বাংলায় একটা কথা আছে, ‘যে যায় লংকায়, সে হয় রাবণ’। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান দুর্বলতা হলো, তাদের দেশ শাসন করার কোনো ধরনের অতীত অভিজ্ঞতা নেই। এই অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তাদের শুরুটা ভালো হয়নি। শুরুতেই তারা একটা হোঁচট খেয়েছে। তারা যদি শুরুতে গণ-অভ্যুত্থানটিকে বিপ্লব হিসেবে আখ্যা দিয়ে যাত্রা শুরু করত, তাহলে ভালো হতো। কিন্তু তারা তো সেটা করেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিজেই ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে নিজের সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন। যেকোনো সরকারপ্রধানের কাছেই প্রথমত জনগণের আস্থা তৈরি হয়। কিন্তু তাঁর প্রতি আস্থাটা জনগণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। যে কারণে গণ-অভ্যুত্থানের পরে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতে যে আস্থাটা ছিল, সেটা সর্বনিম্নে পৌঁছে গেছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলটা গঠিত হয়েছে, সেই দলের লোকজনের নানান ধরনের দুর্নীতি এবং নারী কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। মানে যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তারা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।
এরপর রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি যেটা থাকা দরকার, সেটা আমরা ইউনূস সাহেবের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি নেই বললেই চলে। এ কারণে তাঁকে মাঝেমধ্যে বলতে হয়, তাঁর কথা কেউ শুনছেন না। কিন্তু জনগণ তো একজন সরকারপ্রধানের কাছে সেটা প্রত্যাশা করে না। একজন সরকারপ্রধান কি বলতে পারেন—আমার কথা কেউ শুনছেন না। এ ধরনের কথা কি বাইরে বলার মতো! কিন্তু তিনি তো সেটা বলেছেন প্রকাশ্যে। এ কারণে আমার কাছে মনে হয়, এ সরকারের সফল না হওয়ার পেছনে তাঁর নেতৃত্বের দুর্বলতা সবচেয়ে বড় কারণ। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর শুরুতেই নেতাসুলভ নির্দেশনা দিতে পারেননি।
ধরুন, কোনো সরকারের মন্ত্রিসভায় ২০ জন মানুষ দায়িত্বে আছেন। যে যা-ই বলুক, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো প্রধান ব্যক্তিকেই দিতে হবে। ধরেন, আসিফ নজরুল একটা কাজ করলেন। সেখানে কি সরকারপ্রধান হিসেবে ইউনূস সাহেবের কোনো ভূমিকা থাকবে না। আসিফ নজরুলের কাজটা ঠিক হলো কি না? সেটা তদারকি করার দায়িত্ব পড়ে প্রধান উপদেষ্টার ওপর।
জুলাই আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল, পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা শামিল হয়েছিল। গণ-অভ্যুত্থানের এক বছরের মাথায় তারা কি রাজনীতিতে আগ্রহী, না বিমুখ হচ্ছে?
শিক্ষার্থীরা গণ-অভ্যুত্থানের পরে যেভাবে উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছিল, সত্যিই সেটা এখন কমে গেছে। তারা যখন দেখতে পেল যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এনসিপি গঠিত হলো, তারা সেই পুরোনো ধাঁচেই রাজনীতি করছে। এই দৃশ্য যখন তারা দেখতে পেল, তখন এনসিপির প্রতি তাদের আগ্রহ কমে গেছে। তার সাম্প্রতিকতম প্রমাণ হচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে উমামা ফাতেমার পদত্যাগ। অর্থাৎ এনসিপির প্রতি তাঁর একরকম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এসব মিলিয়ে বলা যায় আন্দোলনে সক্রিয় থাকা অনেক শিক্ষার্থীই রাজনীতির প্রতি আস্থা না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছেন।
আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে একটা বিতর্ক চলছে। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে সবাই একমত না হলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতে পারে?
আমার কাছে মনে হয়, এখনই নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করা হলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির দিকে যাওয়াটা একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যেমন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে আধিপত্যবাদী চরিত্র আছে, সেটা কি এক নিমেষে ধ্বংস করা সম্ভব হবে? আমরা যতই বলি না কেন, সেটা শিগগির শেষ করা সম্ভব নয়। আর এটা পারা সম্ভবও নয়। সে জন্য বলছি, বিএনপির মতো বড় দল কেন আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি মেনে নেবে? কারণ, আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে গেলে তাদের যে আধিপত্য এবং তারা যেভাবে সরকার পরিচালনা করতে চায়, এটা হলে তারা সেটা করতে পারবে না। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হবে। আর আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে অনেক দলই ভোটের শতাংশে সংসদে আসার সুযোগ পাবে। এতে অনেক দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চাইবে। বর্তমান পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে শুধু একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিরোধী দল হবে। আর আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে ১০টি দল বিরোধী দল হবে। এতগুলো দলকে মোকাবিলা করা সরকারি দলের কাছে বেশ চ্যালেঞ্জিং বিষয় হবে।
আমি যেটা বুঝি, বড় দল হিসেবে কোনো দলের যে জায়গায় আধিপত্য খর্ব হবে, সেখানে তারা কোনো ধরনের ছাড় দেবে না। সেই কারণে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখি না।
এখন যদি আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে সব দল ঐকমত্যে না পৌঁছায়, সে ক্ষেত্রে কী করণীয়?
নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য না হলে পরিস্থিতি জটিল হওয়ার কোনো ধরনের সম্ভাবনা দেখি না। এ বিষয়টা সব দলের বুঝতে হবে, নতুবা সমাধানে আসা যাবে না। আর কোনো দল কি এটা নিয়ে বাধ্য করতে পারে? বিএনপির বিরুদ্ধে অন্য দলগুলো এ বিষয়ে কী বলছে, সেটা বিএনপির জন্য ম্যাটার করে না। কারণ, বিএনপি হলো বড় দল। আবার বিএনপি যদি এটা না চায়, তাহলে ঐকমত্য কমিশনের পক্ষে সেটা করা অসম্ভব। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।
নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে না হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াতে পারে?
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে। যারা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন চায়, তারা কিন্তু শক্তিশালী অবস্থানে আছে। শুধু তো বিএনপি এ সময়ে নির্বাচন চাইছে না, অনেক দলই তো ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন চাইছে। এমনকি সেনাবাহিনীও এ সময়ের মধ্যে নির্বাচন চায়। তবে জাতীয় নির্বাচন যদি কোনো কারণে পিছিয়ে যায়, তাহলে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি যে আস্থার জায়গা, সেটা আরও দুর্বল হয়ে যাবে। সে কারণে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। তারপর যদি নির্বাচন এপ্রিল বা জুনে নেওয়া হয়, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়টা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সে সময় এসএসসি পরীক্ষা হয়। জলবায়ুগতভাবে সে সময় তীব্র গরম থাকে। এরপর আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে কি না, এটাও একটা বড় প্রশ্ন? তাই ফেব্রুয়ারিতে যদি নির্বাচন না হয়, তাহলে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।
নির্বাচনীব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন?
একটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তেমন কিছু লাগে না, শুধু সদিচ্ছা থাকলেই সেটা সম্ভব। তবে কিছু আইনকানুনের তো সংস্কার লাগবে। যেমন নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দায়িত্বে কারা থাকবে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শুধু পুলিশ না বিডিআর না সেনাবাহিনী থাকবে, সেটার জন্য ক্লিয়ার ব্যাখ্যা দিতে হবে। আগে নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সেটা বাতিল করে দেয়। এখন কিন্তু সেনাবাহিনীর দায়িত্ব যুক্ত করতে হবে। নতুবা নির্বাচনকালীন ভায়োলেন্স নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আপনাকেও ধন্যবাদ।
জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের এক বছরের মূল্যায়নটা শুনতে চাই।
আমরা দেখেছি জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে শিক্ষার্থী-জনতা, এদের সঙ্গে অনেক রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন পেশার মানুষজন এবং শ্রমজীবী জনগণ যুক্ত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল বৈষম্যের বিরোধিতা। যদিও বৈষম্যের বিরোধিতাটা শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু এর মূল স্পিরিটটা এ দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে। বিগত সময়ের যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা জারি ছিল, সেটাও বৈষম্য সৃষ্টিকারী ছিল। তবে গণ-অভ্যুত্থানের পরে এ দেশের সবার প্রত্যাশা ছিল, আমাদের বাংলাদেশে বৈষম্যহীন সমাজের একটা ছবি সবার কাছে আস্তে আস্তে ভাসতে শুরু করবে। কিন্তু আমরা ক্রমান্বয়ে দেখতে পেলাম অভ্যুত্থানের পরপরই যে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চালু হলো, আমরা সেটার মধ্যে একটা বৈষম্যের রূপ দেখতে পেলাম। বিগত সময়ের সরকার যেভাবে দলীয়করণ করেছিল, আমরা দেখতে পেলাম অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হওয়ার পর একইভাবে দলীয়করণ করা শুরু করল। মানে যারা সরকারের স্টেকহোল্ডার, তাদের রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হলো। সেটা বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি যাদের কথাই বলেন না কেন। আমাদের যে নতুন বাংলাদেশের চিত্র দেখার প্রত্যাশা ছিল, সেটা শুরুতেই বিনষ্ট করা হয়েছে। শুধু বিনষ্ট না, বাধাগ্রস্তও করা হয়েছে। সরকার গঠনের পর শুরুতেই তাদের যে কাজটা করা দরকার ছিল বলে আমি মনে করি, সেটা হলো দেশের মধ্যে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য এক নম্বর গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেশের মানুষকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এখনো করছে। যেটা মব ভায়োলেন্সের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। মব ভায়োলেন্স প্রথম দিকে খুব তীব্র মাত্রায় ছিল। আবার এখন দেখা যাচ্ছে সেটা সারা দেশে আবারও বেড়ে গেছে। সুতরাং আমরা এই সরকারের কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম, সরকার তার অতি সামান্যই সফল করতে পেরেছে। যদিও তারা পাচার করা টাকা উদ্ধারের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের মধ্যে রেমিট্যান্স আসার প্রবাহটা বেড়েছে। কিন্তু অর্থনীতির সম্ভাবনার জায়গাগুলো দুর্বল অবস্থায় পড়ে আছে। বিশেষ করে বিনিয়োগ আসাটা একদম নেই বললে চলে।
অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ হওয়ার কারণ কী বলে মনে করেন?
সাধারণ বাংলায় একটা কথা আছে, ‘যে যায় লংকায়, সে হয় রাবণ’। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান দুর্বলতা হলো, তাদের দেশ শাসন করার কোনো ধরনের অতীত অভিজ্ঞতা নেই। এই অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তাদের শুরুটা ভালো হয়নি। শুরুতেই তারা একটা হোঁচট খেয়েছে। তারা যদি শুরুতে গণ-অভ্যুত্থানটিকে বিপ্লব হিসেবে আখ্যা দিয়ে যাত্রা শুরু করত, তাহলে ভালো হতো। কিন্তু তারা তো সেটা করেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিজেই ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে নিজের সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন। যেকোনো সরকারপ্রধানের কাছেই প্রথমত জনগণের আস্থা তৈরি হয়। কিন্তু তাঁর প্রতি আস্থাটা জনগণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। যে কারণে গণ-অভ্যুত্থানের পরে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতে যে আস্থাটা ছিল, সেটা সর্বনিম্নে পৌঁছে গেছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলটা গঠিত হয়েছে, সেই দলের লোকজনের নানান ধরনের দুর্নীতি এবং নারী কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। মানে যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তারা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।
এরপর রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি যেটা থাকা দরকার, সেটা আমরা ইউনূস সাহেবের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি নেই বললেই চলে। এ কারণে তাঁকে মাঝেমধ্যে বলতে হয়, তাঁর কথা কেউ শুনছেন না। কিন্তু জনগণ তো একজন সরকারপ্রধানের কাছে সেটা প্রত্যাশা করে না। একজন সরকারপ্রধান কি বলতে পারেন—আমার কথা কেউ শুনছেন না। এ ধরনের কথা কি বাইরে বলার মতো! কিন্তু তিনি তো সেটা বলেছেন প্রকাশ্যে। এ কারণে আমার কাছে মনে হয়, এ সরকারের সফল না হওয়ার পেছনে তাঁর নেতৃত্বের দুর্বলতা সবচেয়ে বড় কারণ। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর শুরুতেই নেতাসুলভ নির্দেশনা দিতে পারেননি।
ধরুন, কোনো সরকারের মন্ত্রিসভায় ২০ জন মানুষ দায়িত্বে আছেন। যে যা-ই বলুক, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো প্রধান ব্যক্তিকেই দিতে হবে। ধরেন, আসিফ নজরুল একটা কাজ করলেন। সেখানে কি সরকারপ্রধান হিসেবে ইউনূস সাহেবের কোনো ভূমিকা থাকবে না। আসিফ নজরুলের কাজটা ঠিক হলো কি না? সেটা তদারকি করার দায়িত্ব পড়ে প্রধান উপদেষ্টার ওপর।
জুলাই আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল, পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা শামিল হয়েছিল। গণ-অভ্যুত্থানের এক বছরের মাথায় তারা কি রাজনীতিতে আগ্রহী, না বিমুখ হচ্ছে?
শিক্ষার্থীরা গণ-অভ্যুত্থানের পরে যেভাবে উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছিল, সত্যিই সেটা এখন কমে গেছে। তারা যখন দেখতে পেল যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এনসিপি গঠিত হলো, তারা সেই পুরোনো ধাঁচেই রাজনীতি করছে। এই দৃশ্য যখন তারা দেখতে পেল, তখন এনসিপির প্রতি তাদের আগ্রহ কমে গেছে। তার সাম্প্রতিকতম প্রমাণ হচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে উমামা ফাতেমার পদত্যাগ। অর্থাৎ এনসিপির প্রতি তাঁর একরকম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এসব মিলিয়ে বলা যায় আন্দোলনে সক্রিয় থাকা অনেক শিক্ষার্থীই রাজনীতির প্রতি আস্থা না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছেন।
আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে একটা বিতর্ক চলছে। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে সবাই একমত না হলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতে পারে?
আমার কাছে মনে হয়, এখনই নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করা হলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির দিকে যাওয়াটা একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যেমন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে আধিপত্যবাদী চরিত্র আছে, সেটা কি এক নিমেষে ধ্বংস করা সম্ভব হবে? আমরা যতই বলি না কেন, সেটা শিগগির শেষ করা সম্ভব নয়। আর এটা পারা সম্ভবও নয়। সে জন্য বলছি, বিএনপির মতো বড় দল কেন আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি মেনে নেবে? কারণ, আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে গেলে তাদের যে আধিপত্য এবং তারা যেভাবে সরকার পরিচালনা করতে চায়, এটা হলে তারা সেটা করতে পারবে না। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হবে। আর আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে অনেক দলই ভোটের শতাংশে সংসদে আসার সুযোগ পাবে। এতে অনেক দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চাইবে। বর্তমান পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে শুধু একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিরোধী দল হবে। আর আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে ১০টি দল বিরোধী দল হবে। এতগুলো দলকে মোকাবিলা করা সরকারি দলের কাছে বেশ চ্যালেঞ্জিং বিষয় হবে।
আমি যেটা বুঝি, বড় দল হিসেবে কোনো দলের যে জায়গায় আধিপত্য খর্ব হবে, সেখানে তারা কোনো ধরনের ছাড় দেবে না। সেই কারণে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখি না।
এখন যদি আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে সব দল ঐকমত্যে না পৌঁছায়, সে ক্ষেত্রে কী করণীয়?
নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য না হলে পরিস্থিতি জটিল হওয়ার কোনো ধরনের সম্ভাবনা দেখি না। এ বিষয়টা সব দলের বুঝতে হবে, নতুবা সমাধানে আসা যাবে না। আর কোনো দল কি এটা নিয়ে বাধ্য করতে পারে? বিএনপির বিরুদ্ধে অন্য দলগুলো এ বিষয়ে কী বলছে, সেটা বিএনপির জন্য ম্যাটার করে না। কারণ, বিএনপি হলো বড় দল। আবার বিএনপি যদি এটা না চায়, তাহলে ঐকমত্য কমিশনের পক্ষে সেটা করা অসম্ভব। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।
নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে না হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াতে পারে?
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে। যারা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন চায়, তারা কিন্তু শক্তিশালী অবস্থানে আছে। শুধু তো বিএনপি এ সময়ে নির্বাচন চাইছে না, অনেক দলই তো ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন চাইছে। এমনকি সেনাবাহিনীও এ সময়ের মধ্যে নির্বাচন চায়। তবে জাতীয় নির্বাচন যদি কোনো কারণে পিছিয়ে যায়, তাহলে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি যে আস্থার জায়গা, সেটা আরও দুর্বল হয়ে যাবে। সে কারণে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। তারপর যদি নির্বাচন এপ্রিল বা জুনে নেওয়া হয়, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়টা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সে সময় এসএসসি পরীক্ষা হয়। জলবায়ুগতভাবে সে সময় তীব্র গরম থাকে। এরপর আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে কি না, এটাও একটা বড় প্রশ্ন? তাই ফেব্রুয়ারিতে যদি নির্বাচন না হয়, তাহলে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।
নির্বাচনীব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন?
একটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তেমন কিছু লাগে না, শুধু সদিচ্ছা থাকলেই সেটা সম্ভব। তবে কিছু আইনকানুনের তো সংস্কার লাগবে। যেমন নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দায়িত্বে কারা থাকবে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শুধু পুলিশ না বিডিআর না সেনাবাহিনী থাকবে, সেটার জন্য ক্লিয়ার ব্যাখ্যা দিতে হবে। আগে নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সেটা বাতিল করে দেয়। এখন কিন্তু সেনাবাহিনীর দায়িত্ব যুক্ত করতে হবে। নতুবা নির্বাচনকালীন ভায়োলেন্স নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আপনাকেও ধন্যবাদ।

ড. এম শামসুল আলম একজন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল অনুষদের অধ্যাপক ও ডিন এবং কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা। তিনি অধ্যাপনা করেছেন রুয়েট ও চুয়েটে। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেক গবেষণা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।
৪ ঘণ্টা আগে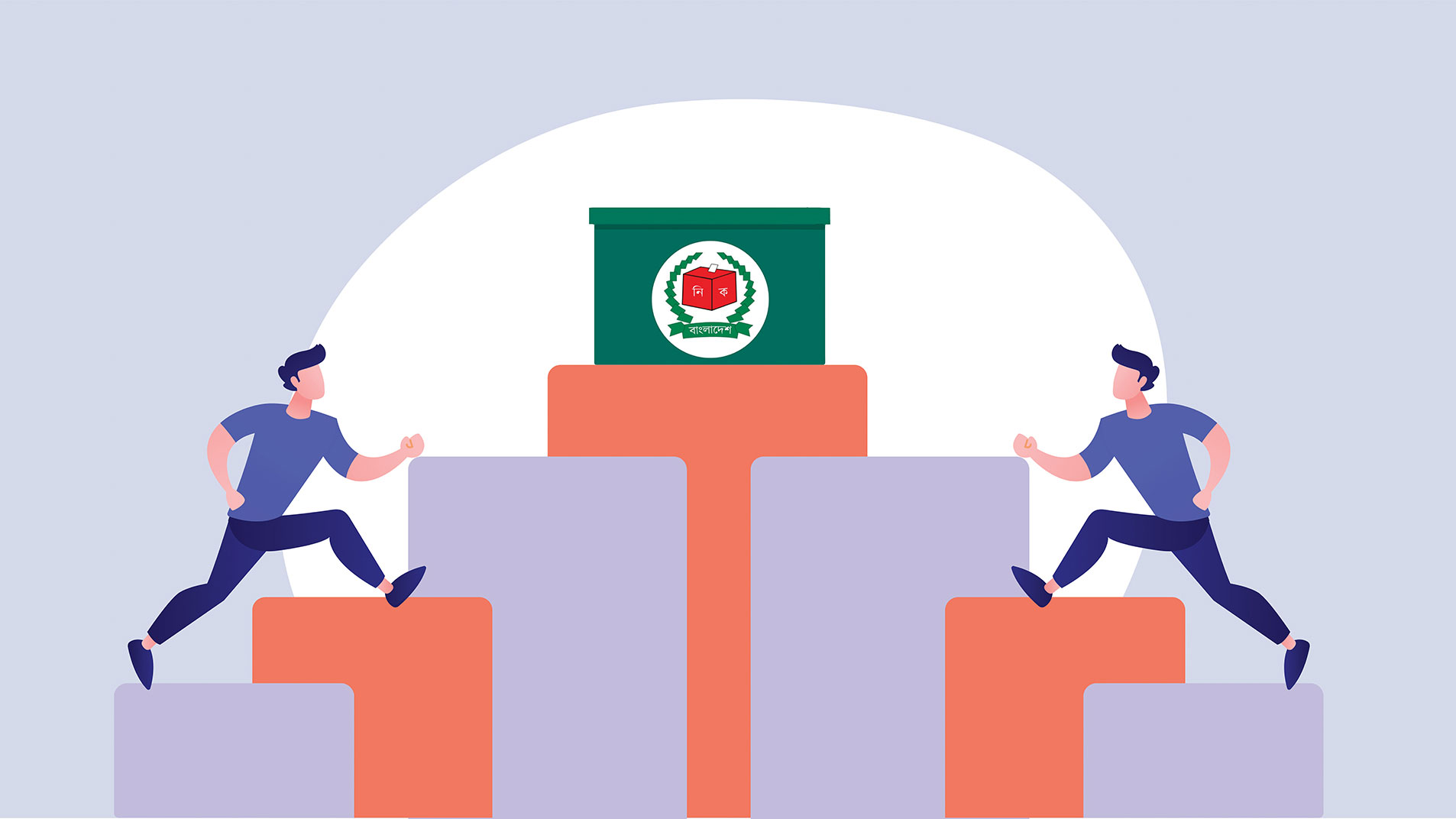
প্রবাদপ্রতিম বাঙালি রাজনীতিক শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ঢাকার এক জনসভায় (১১ জুলাই ১৯৫৮) বলেছিলেন, ‘ইলেকশন বড় মজার জিনিস। এ সময় যে যা-ই বলেন তা-ই সত্য।’ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশে আজ এমনই পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে মনে হচ্ছে।
৪ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল সোমেশ্বরী নদীর ওপর একটি টেকসই সেতু নির্মাণ। সেই স্বপ্ন পূরণে ২৭ কোটি ৩১ লাখ টাকা ব্যয়ে আব্বাসনগর এলাকায় গার্ডার সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ২০২২ সালে।
৪ ঘণ্টা আগে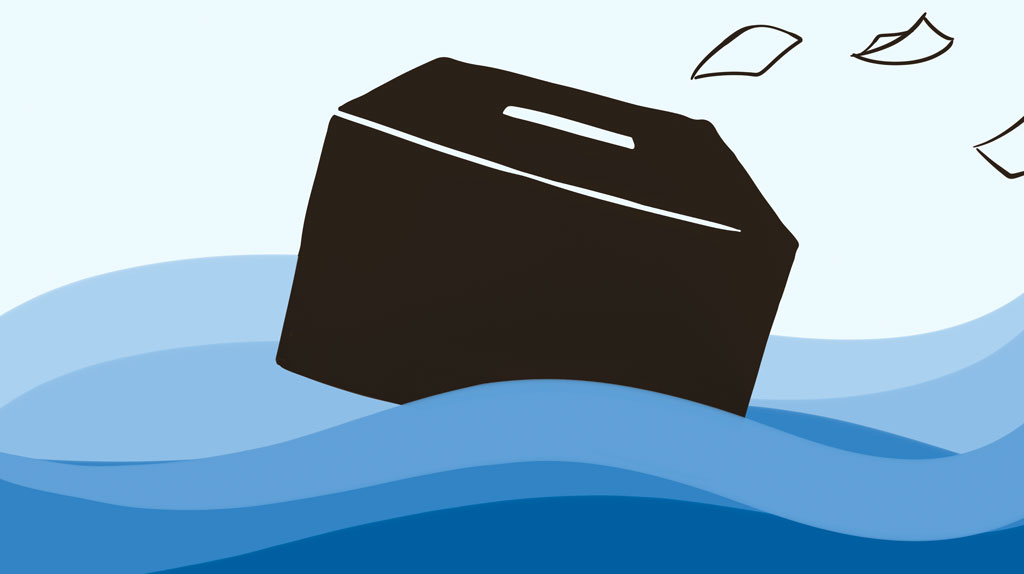
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটের পালে হাওয়া লাগা যাকে বোঝায়, সে রকম কোনো কিছু এখনো সাধারণ জনপরিসরে দেখা যাচ্ছে না। এবারই একসঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে একই দিনে। কিন্তু মানুষকে এখন পর্যন্ত নির্বাচনমুখী হতে দেখা যাচ্ছে না।
১ দিন আগে